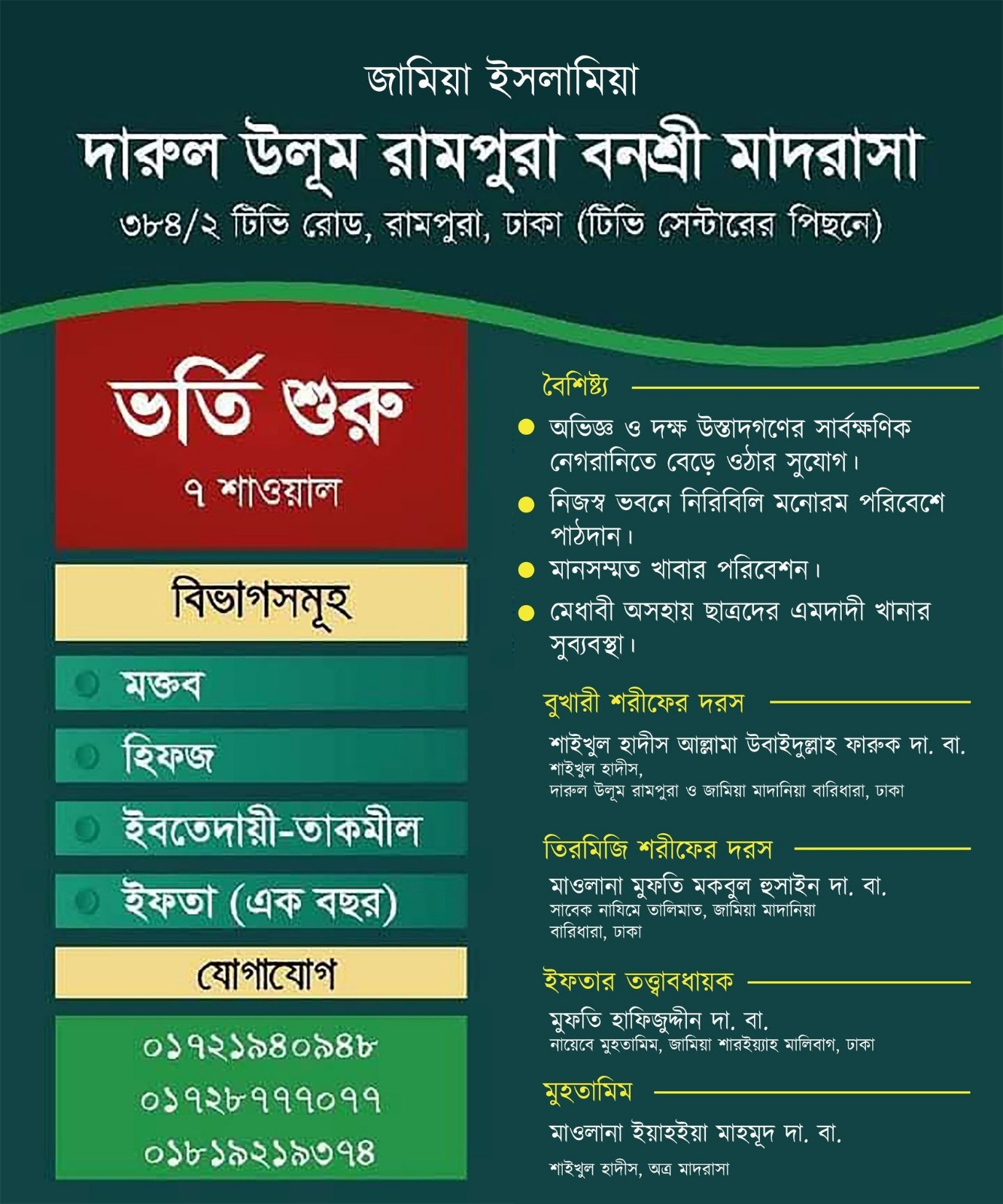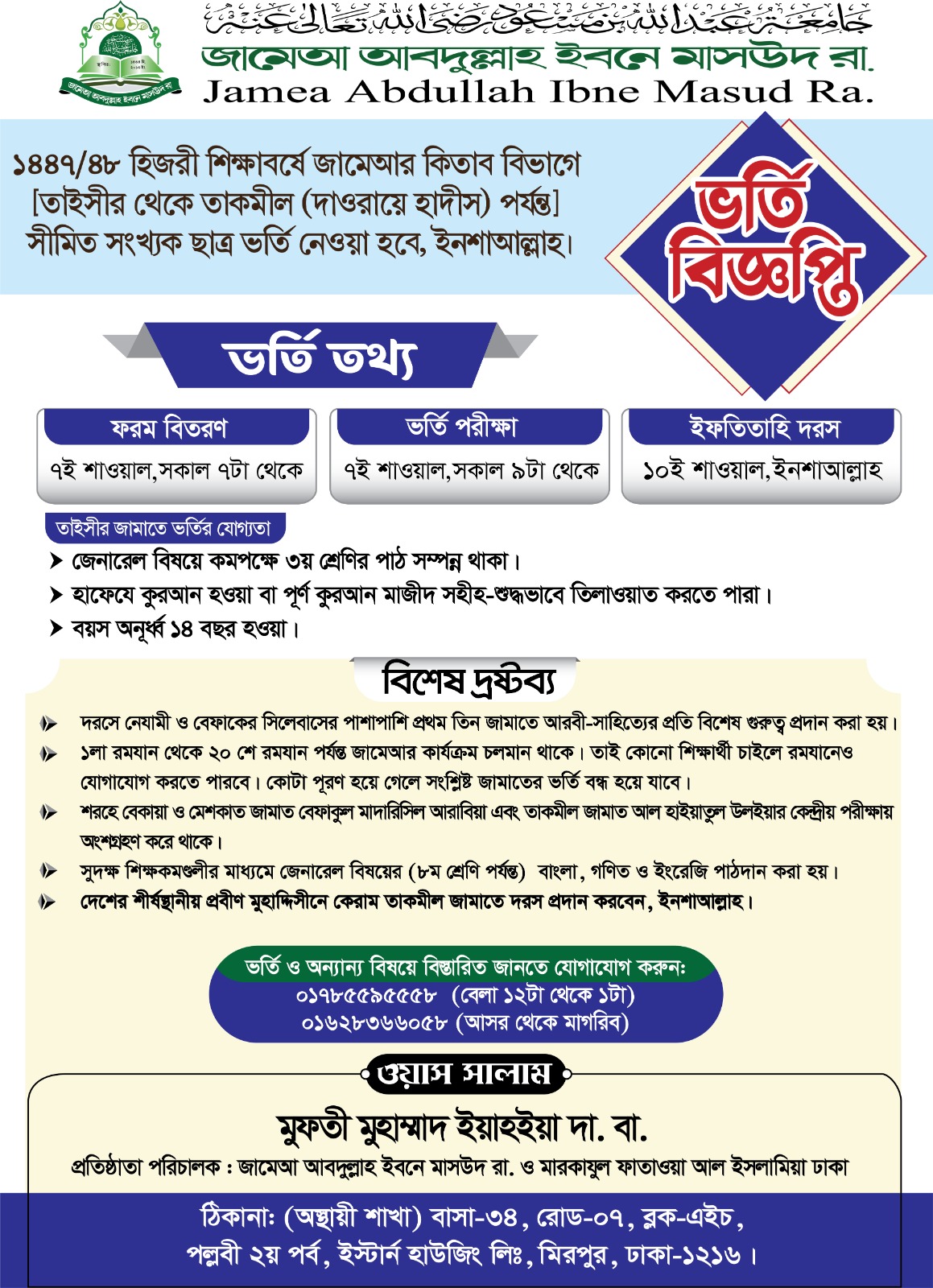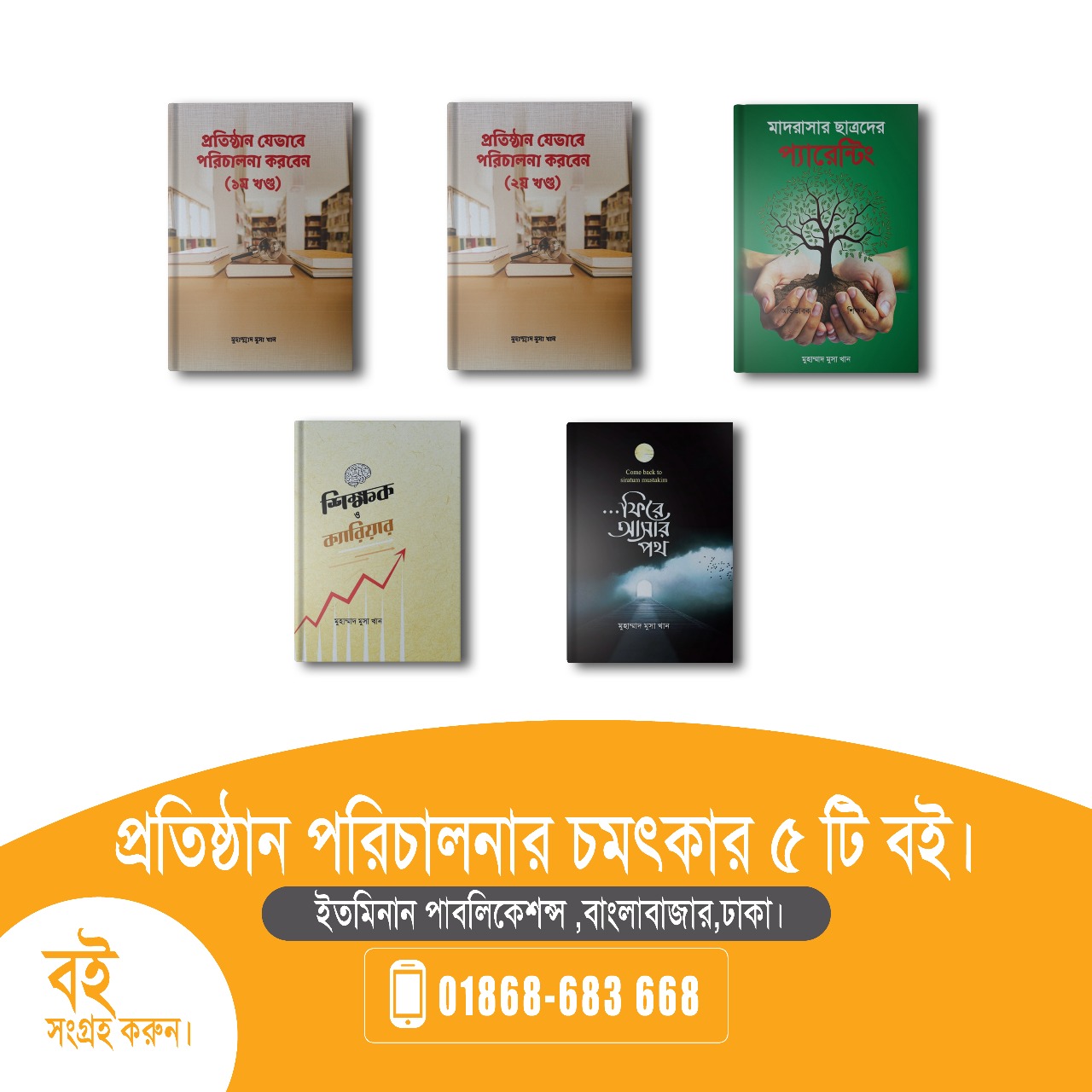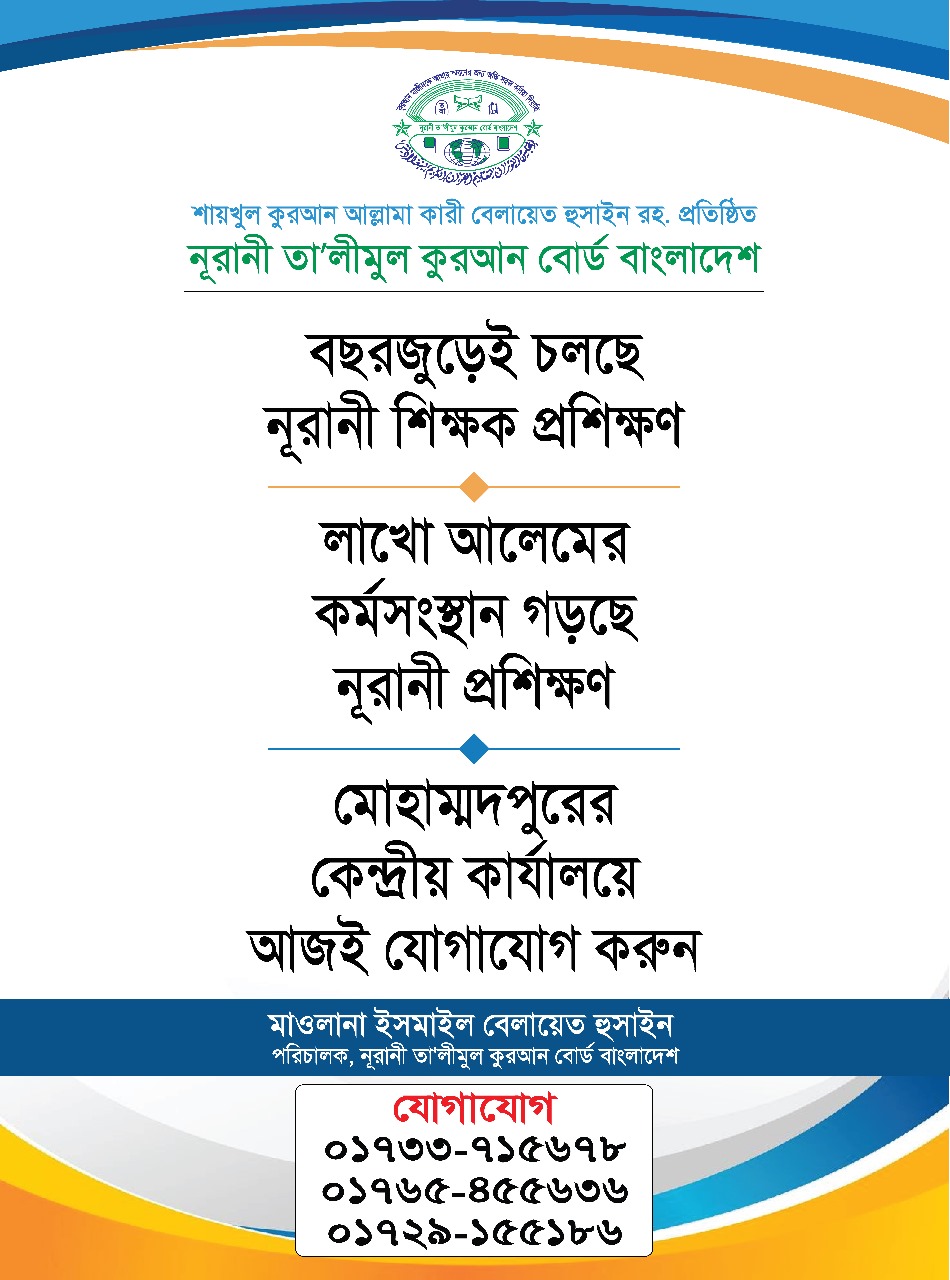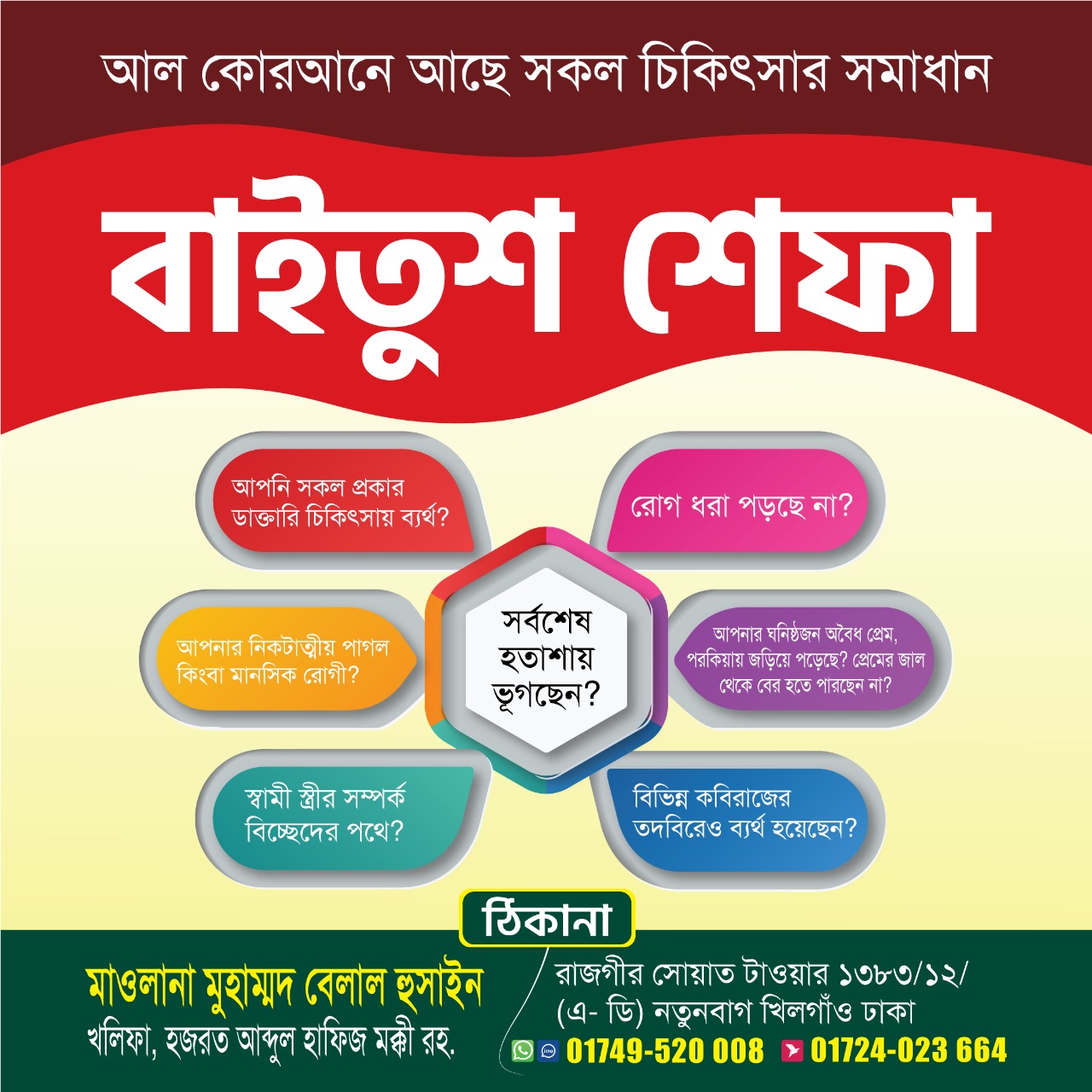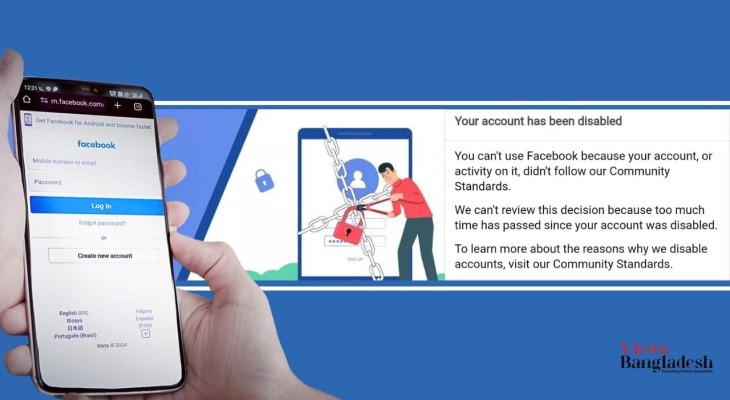ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধের ছবি এবং ভিডিও-তে সয়লাব এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো। অগণিত এসব ছবি এবং ভিডিওর মধ্যে কোনটি সঠিক, আর কোনটি ভুয়া, সেটি বোঝা অনেক ক্ষেত্রেই মুশকিল হয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষের জন্য।
এমনকি এসব ছবি এবং ভিডিও যাচাই করতে গিয়ে মূলধারার গণমাধ্যমগুলোও অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিধায় পড়ে যাচ্ছে।
ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধের যেসব তথ্য আমরা পাচ্ছি, তার একটি বড় অংশই কোন না কোন পক্ষ থেকে দাবিকৃত কিংবা প্রকাশিত খবর। আর এসব তথ্য প্রকাশ করার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে তাদের নিজ নিজ দল বা মতের পক্ষে জোর প্রচারণা চালাতে দেখা যাচ্ছে।
সমর্থন আদায়ের জন্য তারা যেমন কোন ক্ষেত্রে ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর ছবি এবং ভিডিও নিয়ে হাজির হচ্ছেন, তেমনি নানা ষড়যন্ত্র তত্ত্বও দাঁড় করাচ্ছেন।
এমন পরিস্থিতিতে কিছু বিষয় মাথায় রেখে আপনি নিজেই সহজে ভুয়া খবর যাচাই করতে পারেন।
চলুন জেনে নেয়া যাক, কীভাবে ভুয়া খবর যাচাই করবেন...
ভিডিওর স্থান-কাল ও গুণগত মান
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত ছবি বা ভিডিওর স্থান, কাল এবং গুণগত মান যাচাই করে সহজেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, সেটি সঠিক নাকি ভুয়া।
এক্ষেত্রে খবরটি কবে, কখন এবং কোন ভৌগোলিক অবস্থান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত খবরটি যে দেশ বা অঞ্চলকে নিয়ে করা ছবি বা ভিডিওতে সেটির প্রতিফলন আছে কি-না।
ভিডিও বা ছবিতে দেখা যাওয়া এলাকা বা রাস্তার নাম, ব্যবহৃত চিহ্ন, গাড়ির লাইসেন্স প্লেট, বিলবোর্ড বা প্লাকার্ডের লেখা এবং সেটি কোন ভাষায় লেখা, সেটি দেখা যেতে পারে।
এমনকি নির্দিষ্ট ওই ছবি বা ভিডিও ফুটেজের গুণগতমানও আপনাকে ভুয়া খবর যাচাইয়ে সাহায্য করতে পারে।
যেমন - একটি ভিডিওতে দাবি করা হচ্ছে যে, ইসরায়েলি একটি হেলিকপ্টারকে গুলি করে ভূপাতিত করেছে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস।
কিন্তু ভিডিওটি ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে, এটি বেশ ঝাপসা। এর মানে হচ্ছে ভিডিওটি কম্পিউটারে বানানো হয়ে থাকতে পারে।
এই আশঙ্কা থেকেই পরবর্তীতে ভিডিওটি যাচাই করেছে বিবিসি। তাতে দেখা গেছে, এটি আসলে আর্মা ৩ নামের একটি কম্পিউটার গেমস থেকে নেয়া হয়েছে।
খবরটি কে বা কারা প্রকাশ করেছে?
কোন ছবি বা ভিডিও, বিশেষত: সেটি যদি স্পর্শকাতর কোনো বিষয়ের ওপর হয়ে থাকে, তখন খবরটি কে বা কারা প্রকাশ করেছে - সেটি আপনাকে অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে।
খবরটি কোন ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে প্রকাশ হয়ে থাকলে, আপনি সেই প্রোফাইলে ঢুকে প্রথমে দেখবেন ব্যক্তির ভৌগোলিক অবস্থান। তারপর ঘটনাটি যে দেশ বা অঞ্চলের, সেটির সাথে ব্যক্তির ভৌগোলিক অবস্থানের মিল আছে কি-না, সেটি যাচাই করে দেখুন।
যেমন- ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ শুরুর পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত ছবি এবং ভিডিও ফুটেজের অনেকগুলোই প্রকাশিত হয়েছে ভারত এবং পাকিস্তান থেকে।
অথচ যুদ্ধটি হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে। কাজেই ভারত কিংবা পাকিস্তানে বসে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের ভিডিও ধারণ করা কি সম্ভব?
কাজেই ভিডিও বা ছবিটি ভুয়া হবার সম্ভাবনা বেশি।
তাছাড়া ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে দেয়া তথ্যও যাচাই করা যেতে পারে। যেমন যিনি ভিডিওটি প্রকাশ করেছেন, তার পেশা কী? তিনি কি ভিডিওটি প্রকাশ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ?
যদি না হয়ে থাকেন, তাহলে তাকে বিশ্বাস করাটা বোকামী হবে।
আবার অ্যাকাউন্টের টাইমলাইনে প্রকাশিত অন্যান্য ছবি বা ভিডিও দেখেও অনেক সময় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীটির উদ্দেশ্য এবং পক্ষপাতদুষ্টতার ব্যাপারে ধারণা পাওয়া যায়।
যেমন- কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে একই ধরনের ভিডিও বা ছবি বার বার প্রকাশ করা হয়, অথবা স্ববিরোধী ভিডিও বা ছবি প্রকাশ করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে খবরের উৎস হিসেবে সেটি কোনোভাবেই নির্ভরযোগ্য নয়।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে অনেকে বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা ছবি বা ভিডিও প্রচার করে থাকেন।
এক্ষেত্রে কনটেন্টটি প্রথমবার কোন অ্যাকাউন্ট থেকে প্রকাশিত হয়েছে, সেটি পর্যবেক্ষণ করুন। ওই অ্যাকাউন্টের নাম এবং ছবিও যাচাই করুন।
অ্যাকাউন্টটির নামের সাথে যদি একাধিক নম্বর বা বিচ্ছিন্ন অক্ষর দেখতে পান, তাহলে সম্ভাবনা থাকে যে সেটি একটি ভুয়া অ্যাকাউন্ট।
তাছাড়া যদি কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে দিনে গড়ে ৬০-৭০টি কনটেন্ট শেয়ার দেয়া হয়ে থাকে, তাহলেও সেটিকে সন্দেহের তালিকায় রাখতে পারেন।
ভিডিওটি কি আগে কখনো প্রকাশিত হয়েছে?
ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ শুরু পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দাবি করা যাচ্ছে যে, গাজার বাসিন্দারা নিজেদের গায়ে সাদা ব্যান্ডেজ বেঁধে তার ওপর লাল রঙ দিয়ে নিজেদেরকে আহত বলে উপস্থাপন করছেন।
কিন্তু ভিডিওটি যাচাই করে দেখা গেছে যে, সেটি আসলে একটি ফিলিস্তিন চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় মেকআপ রুমে ধারণ করা এবং ২০১৭ সালেই ভিডিওটি প্রথমবার ইউটিউবে প্রকাশ করা হয়েছিল।
কাজেই এরকম কোনো ছবি বা ভিডিও আপনার সামনে আসলে, সেটি বিশ্বাস করার আগে খুঁজে দেখুন সেটি প্রথমবার কবে প্রকাশিত হয়েছে।
এক্ষেত্রে গুগল, বিঙ, টিনআই এবং ওয়ানডেক্সের মতো সার্চ ইঞ্জিনগুলো আপনাকে সাহায্য করবে।
সন্দেহজনক ভিডিও বা ছবি ধরে সার্চ ইঞ্জিনগুলোতে দিলেই সেটি আগে প্রকাশিত হয়েছে কি-না, এবং হয়ে থাকলে কবে, কোথায়, কে বা কারা প্রকাশ করেছে, সেটি জানা হয়ে যাবে।
নকল ভুক্তভোগী থেকে সাবধান
গত সাতই অক্টোবর ইসরায়েলের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়ে হত্যার পাশাপাশি বেশ কয়েকজন ইসরায়েলি নাগরিককে জিম্মি করে হামাস। এ ঘটনার কিছু ভিডিও প্রকাশ হয়।
কিন্তু এরপর অনেকেই কাছাকাছি ধরনের ভিডিও প্রকাশিত করে নিজেদেরকে ভুক্তভোগী হিসেবে উপস্থাপন করতে থাকেন।
ইসরায়েলি নাগরিককে জিম্মি করার ভিডিও ফুটেজের নিচেও অনেকে কমেন্ট করে নিজেই এভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা পরবর্তীতে নকল বা সাজানো ঘটনা বলে প্রমাণিত হয়েছে।
দেখা গেছে, হামলার ঘটনায় নতুন মাত্রা যুক্ত করার উদ্দেশ্যে অনেকে টাকার বিনিময়েও এমনটি করেছেন। যেমন- একটি ভিডিওতে বলা হচ্ছিলো যে, তিনি এখন গাজায় হামাসের হাতে জিম্মি।
অথচ ভিডিওটি ধারণ করা হয়েছে ইসরায়েলের একটি রাস্তার ধারে।
এরকম নকল ও সাজানো ভুক্তভোগীদের বিষয়েও সাবধান থাকতে হবে। এছাড়া প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য চোখ রাখতে হবে খবরের নির্ভরযোগ্য মাধ্যমগুলোতে।
ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে কতজনকে জিম্মি করেছে, যারা জিম্মি হয়েছেন তাদের পরিচয় কী? তাদের পরিবার-পরিজন বা বন্ধু-বান্ধবের বক্তব্য, প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান ইত্যাদির পাশাপাশি ঘটনার জন্য কাদেরকে দায়ী করা হচ্ছে- সকল তথ্যই ইতিমধ্যে মূলধারার গণমাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে।
কাজেই একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর দেখার পাশাপাশি একটির সাথে অন্যটির তথ্য মিলিয়ে দেখলেই প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে আপনি একটি স্বচ্ছ ধারনা পাবেন।
সেটি না করে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিও বা ছবির কিংবা সেগুলোর কমেন্ট শাখায় প্রকাশিত তথ্য বিশ্বাস করাটা বোকামী হবে।
পোস্টের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভাবুন
স্পর্শকাতর যেকোনো ইস্যুতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভাইরাল পোস্ট পড়ার পর আপনার মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এবং এটি দেখলে অন্যদের ভেতর কেমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটি ভাবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
কেননা, মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ করে সহজেই অন্যের আবেগ ও বিশ্বাস নিয়ে খেলা যায়। আর এক্ষেত্রে আবেগের বসে অনেকেই ভুয়া খবর শেয়ার করতে থাকেন।
যেমনটি ঘটেছে ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ শুরুর পর।
দু-পক্ষের সমর্থকদের অনেকেই দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে ভুয়া ভিডিও এবং ছবি শেয়ার করেছেন। এতে বিদ্বেষ বেড়েছে এবং পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে গেছে।
কাজেই স্পর্শকাতর যেকোনো ইস্যুতে ছবি বা ভিডিও প্রকাশ বা শেয়ার করার ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রশ্ন তুলতে হবে সেটির যথার্থতা ও উৎস নিয়ে।
এমনকি আপনার পরিচিতজন বা কাছের আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবও কোনো পোস্ট বা তথ্য শেয়ার করেছে বলে, আপনারও সেটি চোখ বুজে শেয়ার করাটা উচিত হবে না।
শেয়ার করার আগে একটু থামুন।
দ্বিতীয়বার ভাবুন এবং খবরের যথার্থতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিন।
ওয়েবসাইটের খবরও যাচাই করা
কোন অনলাইন বা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত খবর নিয়েও যদি সন্দেহ হয়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই খবরটি যাচাই করুন।
ওয়েবসাইটটি সম্পর্কে আগে খোঁজ নিন। ওয়েবসাইটটি কতদিন আগে নিবন্ধিত হয়েছে, কারা সেটি তৈরি করেছেন - যাচাই করুন।
এক্ষেত্রে ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর অ্যাসাইনড নেমস অ্যান্ড নাম্বারস ICANN এবং হুইজডটকম Whois.com আপনাকে সাহায্য করবে।
এর বাইরে ভুয়া খবর নিশ্চিত হতে নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগান।
সূত্র: বিবিসি
কেএল/