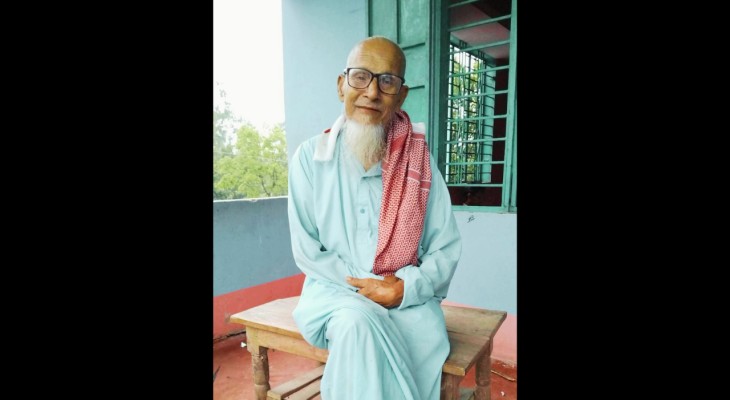ছবির ক্যাপশান,দেশ রূপান্তর
মানবজমিনের প্রধান শিরোনাম, 'মব সন্ত্রাস চলছেই, নিষ্ক্রিয় প্রশাসন: এই মৃত্যুর দায় কার?'
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ৫ই অগাস্ট সরকার পতনের পর থেকে দেশে একের পর এক মব (জনতা দ্বারা সংঘটিত) সহিংসতা চলছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শুরুতে নিরুপায় ছিল এবং প্রশাসনও ছিল নিষ্ক্রিয়।
যদিও পরে সশস্ত্র বাহিনী ও অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়, তবুও এক বছরের মধ্যেও মব সন্ত্রাস থামেনি। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, এই সময়ে অন্তত ১৭৪ জন মব হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন।
কুমিল্লার মুরাদনগরে এক পরিবারের তিন সদস্যকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা দেশজুড়ে চরম উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। একইভাবে পাটগ্রাম থানায় হামলা চালিয়ে আসামি ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনা পুলিশ প্রশাসনের অকার্যকারিতা প্রকাশ করেছে।
সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস ও লুটের ঘটনা ঘটেছে, আহত হয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তাসহ অনেক মানুষ। এ ঘটনায় বিএনপিকে জড়ানোর অভিযোগ হলেও, দলটি তা অস্বীকার করেছে।
অন্যদিকে, চট্টগ্রামে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের জেরে এনসিপি আওয়ামী আমলে নিয়োগ পাওয়া ওসিদের বরখাস্তের দাবি তুলেছে এবং পুলিশের সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছে।
প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, অপরাধীদের বিচারহীনতা এবং রাজনৈতিক অসন্তোষের মধ্যে আগামী জাতীয় নির্বাচনের পরিবেশ নিয়েও শঙ্কা তৈরি হয়েছে।
মানুষ প্রশ্ন করছে, এসব মৃত্যুর দায় কার? বিচার ও জবাবদিহিতা না থাকলে আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা আরও বাড়বে।

সমকালের প্রধান শিরোনাম, 'নির্বাচনী কার্যক্রম দানা বাঁধছে না, পথ স্পষ্ট নয়'
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) প্রস্তুতি এখনো পরিষ্কার নয়। একটি স্বচ্ছ ভোটার তালিকা ও সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
আইন সংশোধন হলেও সীমানা পুনর্নির্ধারণ এবং ভোটার তালিকার কাজ চলমান রয়েছে। ভোটের জন্য কেন্দ্রে প্রস্তুতি, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও নতুন দলের নিবন্ধনসহ নানা বিষয় এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাবে ইসির কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিলেও সময় ও পদ্ধতি নিয়ে দলগুলোর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।
বিএনপি বর্তমান সীমানা মানতে চায় না এবং ২০০১ সালের আগের সীমানা ফেরত চায়, যা বিশ্লেষকদের মতে এখন আর বাস্তবসম্মত নয়।
ইসি ফেব্রুয়ারি বা এপ্রিল, এই দুই সময়ই নির্বাচন হতে পারে ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছে।
ভোটার তালিকার হালনাগাদে ইতোমধ্যে প্রায় ৫৯ লাখ নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছে এবং ৪৩ লাখের বেশি নতুন ভোটারকে নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়ার উদ্যোগ চলছে।
জুলাই মাসে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি 'জুলাই সনদ' হওয়ার কথা থাকলেও কিছু বিষয়ে দ্বন্দ্ব এখনো কাটেনি। তবু আশা করা হচ্ছে, সময়মতো সমাধান এলে নির্বাচন আয়োজনের পথ সুগম হবে।

কালের কণ্ঠের প্রধান শিরোনাম, 'চালের দামে দিশাহারা ভোক্তা'
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, সারা দেশে চালের দাম বাড়ায় সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ঢাকার খুচরা বাজারে মিনিকেট চালের কেজিতে আট থেকে ১০ টাকা, আর মাঝারি ও মোটা চালের দাম তিন থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।
চট্টগ্রাম ও দিনাজপুরেও চালের ৫০ কেজির বস্তায় ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত দাম বেড়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, মিল পর্যায়ে সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ানো হয়েছে, আর ধান ও পরিবহন খরচ বাড়ার কারণে দাম বাড়ছে বলে দাবি মিল মালিকদের।
রাজধানীর বাজারে এখন মিনিকেট চাল প্রতি কেজি ৮২-৯০ টাকা, ব্রি-২৮ ও পাইজাম চাল ৬০-৬৪ টাকা, যা ঈদের আগে ছিল অনেক কম।
সবজির দামও চড়া—প্রায় সবজির কেজি ১০ থেকে ২০ টাকা বেড়েছে। কাঁচা মরিচ, টমেটো, করলা, বেগুন, শসা—সবকিছুতেই অস্থিরতা। মুরগি, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন, ডাল, সব কিছুর দাম ঊর্ধ্বমুখী।
চট্টগ্রামে 'ভাতের পাতে স্বস্তি ফেরাও' স্লোগানে মানববন্ধন হয়েছে।
দিনাজপুর, নওগাঁসহ বিভিন্ন জেলায় চালের পাইকারি দাম বেড়ে খুচরা বাজারেও প্রভাব পড়েছে।
চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে না থাকায় সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের শ্রেণি চরম কষ্টে পড়েছে। ভোক্তাদের অভিযোগ—সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

প্রথম আলোর প্রধান শিরোনাম, '৮০% মামলায় অভিযোগপত্র জমা'
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, গত এক বছরে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ৩৯৯টি দুর্নীতির মামলা করেছে, যার মধ্যে ৮০ শতাংশ মামলায় অভিযোগপত্র আদালতে জমা হয়েছে।
এসব মামলার আসামির তালিকায় রয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার পরিবার, সাবেক মন্ত্রী, এমপি, আমলা, পুলিশ কর্মকর্তা ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা।
অভিযোগ রয়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার, অবৈধ সম্পদ অর্জন, টাকা পাচার, টেন্ডারবাজি ও শেয়ারবাজার প্রতারণার মাধ্যমে হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।
শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে জমি বরাদ্দে অনিয়ম, বিদেশে টাকা পাচার ও বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে একাধিক মামলা হয়েছে।
টিউলিপ সিদ্দিক ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে।
দুদক বলছে, আগের সরকারগুলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলেও গণ–অভ্যুত্থানের পর তদন্তে গতি এসেছে।
বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে তারা উদ্যোগ নিয়েছে এবং এর অংশ হিসেবে অনেক সম্পত্তি জব্দ করা হয়েছে। যুক্তরাজ্য, দুবাই, যুক্তরাষ্ট্রে সম্পদ কিনেছেন এমন প্রমাণও মিলেছে।
আদালতের আদেশে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করা হয়েছে।
তবে দুদকের কিছু কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন, দ্রুত মামলা করতে গিয়ে তদন্তে ভুল হয়েছে, যা ভবিষ্যতে শাস্তি নিশ্চিত করতে বাধা হতে পারে। এখন প্রয়োজন সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করা।

দ্য ডেইলি স্টারের প্রধান শিরোনাম, 'Panic grips NBR officials' অর্থাৎ, 'এনবিআর কর্মকর্তাদের মধ্যে আতঙ্ক'
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধর্মঘট শেষে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও এখন আবার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
সরকার বেশ কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তাকে অবসরে পাঠিয়ে এবং দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) নতুন তদন্ত শুরু করায় এনবিআরের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে।
এরইমধ্যে ১৬ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত চলছে, যাদের অনেকেই ধর্মঘটকারী প্ল্যাটফর্ম 'রিফর্ম ইউনিটি কাউন্সিল'-এর সঙ্গে যুক্ত।
ধর্মঘটের কারণে জুনের শেষ সপ্তাহে চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে, যা দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ক্ষতি ডেকে আনে।
ব্যবসায়ী নেতারা আন্দোলন বন্ধে মধ্যস্থতা করে সরকারি আশ্বাসে কর্মকর্তাদের কাজে ফেরান। কিন্তু পরবর্তীতে সরকার যেভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়, তাতে ব্যবসায়ী মহলও বিব্রত।
তারা বলেন, যদি এই ধরনের কঠোর অবস্থান না নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হতো, তবে পরিস্থিতি ভালো থাকত।
এভাবে হঠাৎ অবসরে পাঠানো, তদন্ত, জব্দ আদেশ ইত্যাদি এনবিআরের দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে, যার ফলে পুরো সংস্থার কার্যকারিতা ঝুঁকিতে পড়েছে। এখন এনবিআরের ভেতরে নেতৃত্ব সংকট দেখা দিয়েছে।
ব্যবসায়ী নেতারা আবারও সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, যেন সংশ্লিষ্ট সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে আলোচনা করে অংশগ্রহণমূলক সংস্কার প্রক্রিয়া চালানো হয়, যাতে অর্থনীতির ক্ষতি কমানো যায় এবং ভবিষ্যতে এমন সংকট এড়ানো যায়।

আজকের পত্রিকার প্রধান শিরোনাম, 'বরখাস্তের দণ্ড বদলে বাধ্যতামূলক অবসর'
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, সরকার চলমান আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকারি চাকরি অধ্যাদেশ সংশোধন করছে। আগে অসদাচরণের জন্য সরকারি কর্মচারীদের বরখাস্ত বা অপসারণ করা যেত, এখন তা বাদ দিয়ে বাধ্যতামূলক অবসরের বিধান রাখা হচ্ছে।
এতে কর্মচারীরা পেনশনসহ সব আর্থিক সুবিধা পাবেন। 'অনানুগত্য' ও 'অনুপস্থিতির জন্য উসকানি' ধারা বাদ যাচ্ছে।
অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যেখানে একজন নারী সদস্য থাকবেন।
তদন্তের সময়সীমা ১৪ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে, না মানলে কমিটির সদস্যদের দায়ী করা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অবসরের সিদ্ধান্তে ৩০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে আপিলের সুযোগ থাকবে।
আন্দোলনকারীদের দাবি অনুযায়ী এই সংশোধন আনা হচ্ছে। কারণ দর্শানোর সুযোগ, নারী অন্তর্ভুক্ত তদন্ত কমিটি এবং শৃঙ্খলা বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশোধন করা হচ্ছে।
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে না জানিয়ে অনুপস্থিত থাকলেও তা শাস্তিযোগ্য হবে না, এ রকম ব্যাখ্যাও যুক্ত হচ্ছে।
সচিবালয়ের আন্দোলনরত কর্মচারীরা বলছেন, তাদের প্রস্তাব মেনে নেওয়ায় আশঙ্কা অনেকটাই কেটে গেছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, যদিও উদ্যোগটি ইতিবাচক, তবু স্থানীয় সরকার বা সিটি করপোরেশনের কর্মচারীদের জন্য আলাদা আইন না থাকায় দ্বৈততা তৈরি হতে পারে।
তাই কেউ কেউ মনে করেন, এই অধ্যাদেশ বাতিল করে একটি নতুন, শক্তিশালী ও স্পষ্ট আইন করা প্রয়োজন ছিল।

নয়া দিগন্ত প্রধান শিরোনাম, 'বিভাগে হাইকোর্টের বেঞ্চ'
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে সংলাপে অংশ নিয়ে দেশের প্রায় ৩০টি রাজনৈতিক দল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে।
আলোচনা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ রাজধানীর বাইরে সব বিভাগীয় শহরে প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমার ক্ষমতা সীমিত করার বিষয়ে।
রাজনৈতিক দলগুলো মনে করছে, বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ হলে সাধারণ মানুষের কাছে বিচার আরও সহজে পৌঁছাবে।
তবে এর জন্য পর্যাপ্ত বিচারপতি ও দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ এবং বাজেট বাড়ানোর পরামর্শও এসেছে।
রাষ্ট্রপতির ক্ষমার বিষয়ে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে অপরাধীকে ক্ষমা করতে হলে ভুক্তভোগী পরিবারের মতামত নিতে হবে। ক্ষমার আগে একটি নির্দিষ্ট কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হবে।
এতে রাজনৈতিক অপব্যবহার বন্ধ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপি দু'টি বিষয়েই একমত হয়েছে।
তারা বলেছে, বিচারব্যবস্থায় ফ্যাসিস্ট প্রভাব দূর করতে হবে এবং যেসব কর্মকর্তা অন্যায়ভাবে মানুষকে সাজা দিয়েছেন, শুধু চাকরি হারালে হবে না—তাদের বিচারের মুখোমুখিও করতে হবে।
আলোচনায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে বলে নীতিগত সম্মতি হয়। সংলাপে জামায়াত, বিএনপি, বাসদ, সিপিবি, এবি পার্টিসহ ৩০টি দল অংশ নেয়।
আগামী সপ্তাহে পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রগতি আশা করা হচ্ছে।

ঢাকা ট্রিবিউনের প্রধান শিরোনাম, 'How suitable is the PR system for Bangladesh?' অর্থাৎ, বাংলাদেশের জন্য আনুপাতিক পদ্ধতি কতটা উপযুক্ত?
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার দাবি উঠেছে, বিশেষ করে প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর) বা অনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক চলছে। বর্তমানে দেশে এফপিটিপি পদ্ধতি চালু, যেখানে সর্বাধিক ভোট পাওয়া প্রার্থী জেতেন।
কিন্তু আনুপাতিক ব্যবস্থায়, দলভিত্তিক ভোট গণনা হয় এবং যে দল যত শতাংশ ভোট পায়, সেই অনুপাতে তারা আসন পায়। ফলে ছোট দলগুলোরও সংসদে জায়গা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।
ইসলামী আন্দোলন, জামায়াত ও গণ-অধিকার পরিষদ পিআর ব্যবস্থার পক্ষে বললেও, বিএনপি এর বিরোধিতা করেছে।
বিএনপির মতে, এই পদ্ধতি দুর্বল সরকার তৈরি করবে এবং পুরনো স্বৈরশাসকদের ফিরে আসার সুযোগ তৈরি করবে। তাদের আশঙ্কা, এতে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়বে।
ইতিহাস বলছে, ১৯৭৩ ছাড়া আর কোনো জাতীয় নির্বাচনে কোনো দলই ৫০ শতাংশ ভোট পায়নি। ফলে পিআর ব্যবস্থা চালু হলে বহু নির্বাচনেই জোট সরকার গঠন হতো।
ইউরোপের কিছু দেশে পিআর সফল হলেও, ইতালি ও ইসরায়েলের মতো দেশগুলোতে এটি রাজনৈতিক অস্থিরতা ডেকে এনেছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা আনুপাতিক পদ্ধতির জন্য এখনো প্রস্তুত নয়। চাইলে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু আসনে এ পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে, তবে পুরোপুরি নয়।

বণিক বার্তার প্রধান শিরোনাম, 'অন্তর্বর্তী সরকারের খসড়া টেলিকম নীতিমালা নিয়ে শুরু হলো বিতর্ক'
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, সরকার ২০২৫ সালের জন্য প্রস্তাবিত নতুন টেলিকম নীতিমালা প্রকাশের পর দেশে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছে।
সরকারের দাবি, এই নীতিমালা ভয়েস কল ও ইন্টারনেটের খরচ কমাবে, অবকাঠামো ভাগাভাগির মাধ্যমে সাশ্রয়ী ও টেকসই ডিজিটাল ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।
অন্যদিকে, খাতসংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এতে দেশীয় ছোট উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানগুলো বিপদে পড়বে, কর্মসংস্থান হারাবে এবং বাজারের নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে বড় মোবাইল অপারেটর ও বিদেশি কোম্পানির হাতে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন লাইসেন্স কাঠামো অনুসারে পুরনো অনেক প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হবে, যার প্রভাব পড়বে কয়েক লাখ কর্মজীবীর ওপর।
আইএসপি সংগঠনসহ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অভিযোগ করছে, এ নীতিমালায় তাদের মতামত নেওয়া হয়নি এবং এটা বাস্তবায়িত হলে বড় ব্যবসাগোষ্ঠীর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বাড়বে।
বিএনপি বলছে, তাড়াহুড়ো করে নীতিমালা তৈরি না করে, আগে আর্থিক ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করে এবং সবার অংশগ্রহণে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এটি এখনও খসড়া এবং সকল পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে পরিবর্তন আনা সম্ভব।
সব মিলিয়ে বিতর্কের মূল বিষয় হলো, এই নীতিমালা গ্রাহক সেবা উন্নয়নে সহায়ক হবে, নাকি দেশীয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থানের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

নিউ এজের প্রধান শিরোনাম, '15 lakh COVID jabs unused, set to expire in Bangladesh by August 6' অর্থাৎ, 'বাংলাদেশে ১৫ লাখ কোভিড টিকা অব্যবহৃত, ৬ অগাস্টের মধ্যে মেয়াদ ফুরাবে'।
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে মে মাস থেকে অব্যবহৃত থাকা ১৫ লাখের বেশি ফাইজার কোভিড টিকার মেয়াদ ৬ই অগাস্টের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।
জনগণের অনীহার কারণে এসব টিকা ব্যবহার করা যাচ্ছে না, যদিও দেশে নতুন করে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার বাড়ছে। টিকাদান কর্মীরা মানুষকে বিনামূল্যে টিকা নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করলেও সাড়া খুবই কম।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, এ বছর এখন পর্যন্ত ৩০ লাখের বেশি টিকা সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৭ লাখ বিতরণ করা হয়েছে এবং সেগুলো ২২শে জুলাই থেকে ৬ই অগাস্টের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ হবে। বাকিগুলো নভেম্বরের শুরুতে শেষ হয়ে যাবে।
চট্টগ্রামে ৭৪ হাজার টিকার মধ্যে এখনো ১৪ হাজারেরও কম টিকা দেওয়া হয়েছে, যদিও এই অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ও সংক্রমণ হয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টিকার কার্যকারিতা অনেকাংশে সংরক্ষণের উপর নির্ভর করে, যা উপজেলা পর্যায়ে সমস্যা সৃষ্টি করছে। টিকা না নেওয়ার পেছনে জনগণের অনীহা এবং সচেতনতার অভাবই প্রধান কারণ।
সরকার ও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বলছে, টিকা পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, কিন্তু মানুষ আগ্রহ দেখাচ্ছে না। উন্নয়ন সহযোগীরা অর্থ দেওয়া বন্ধ করায় সচেতনতামূলক প্রচারও ব্যাহত হচ্ছে। এখনো করোনা নিয়ন্ত্রণে টিকা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
এনএইচ/
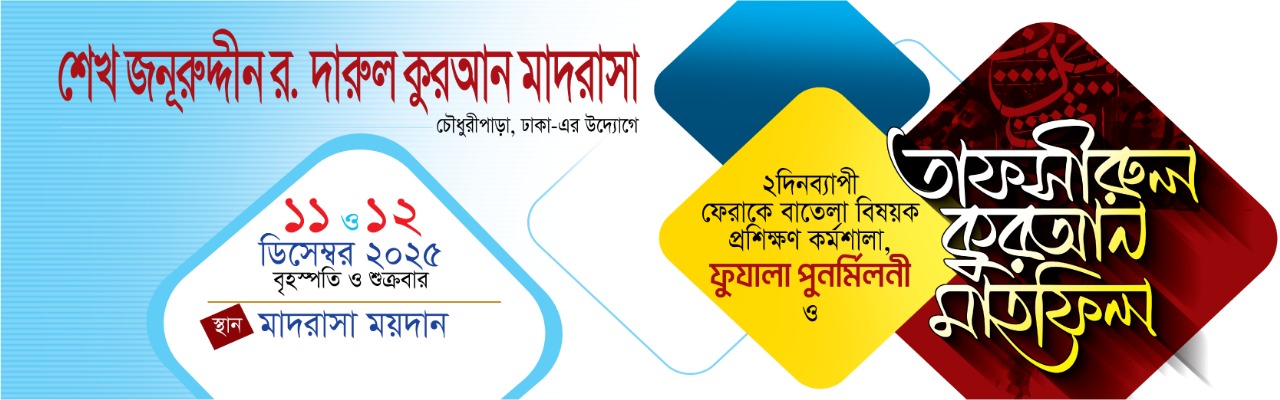
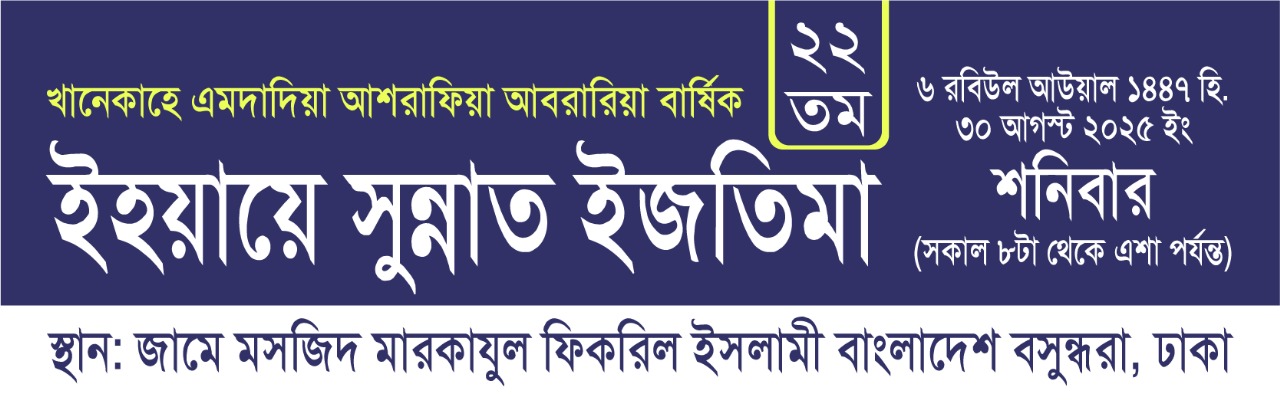


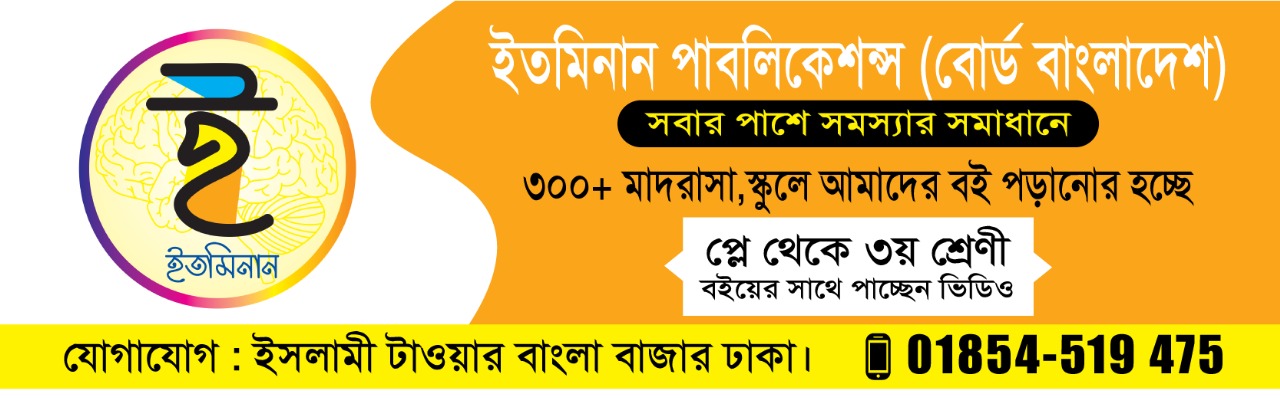


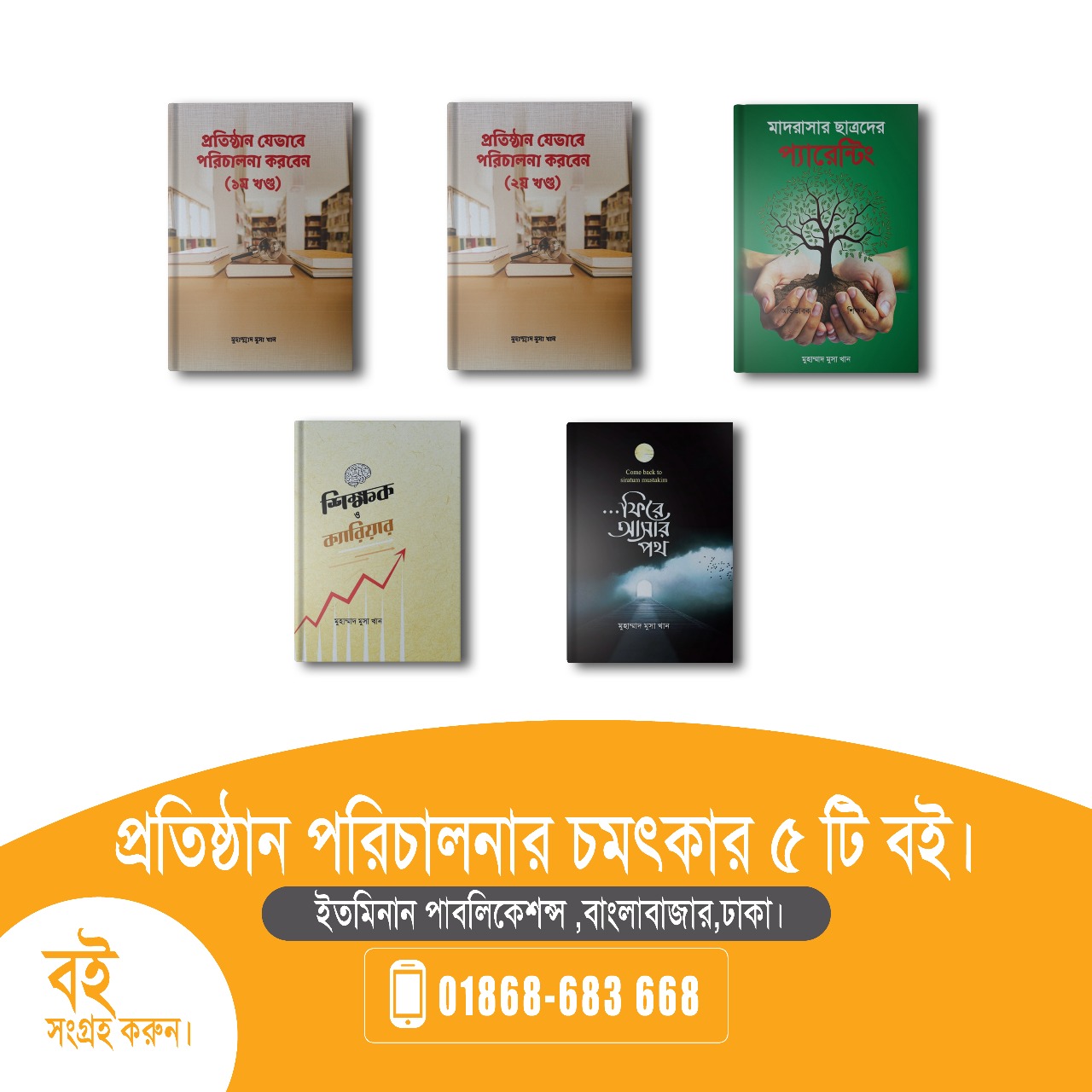
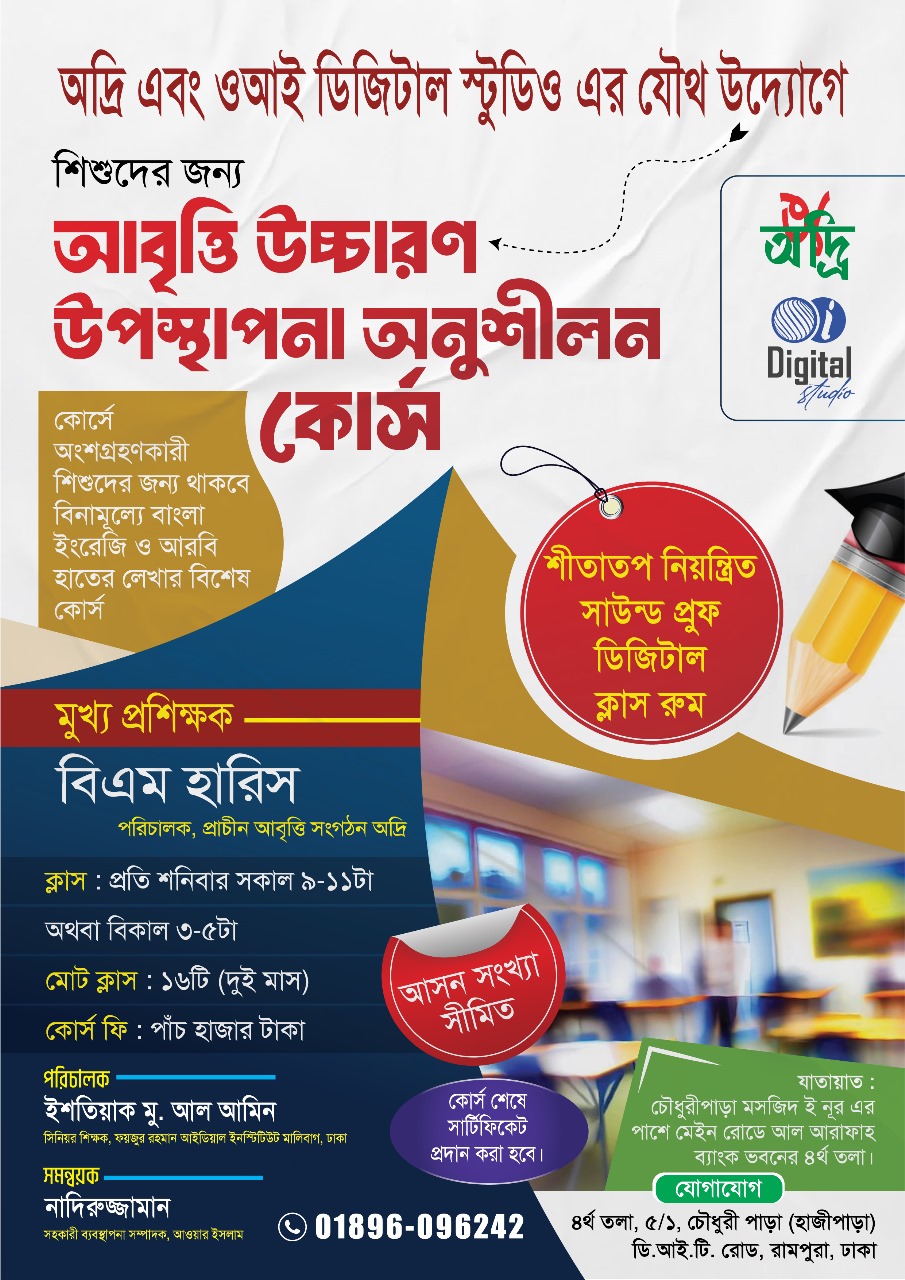

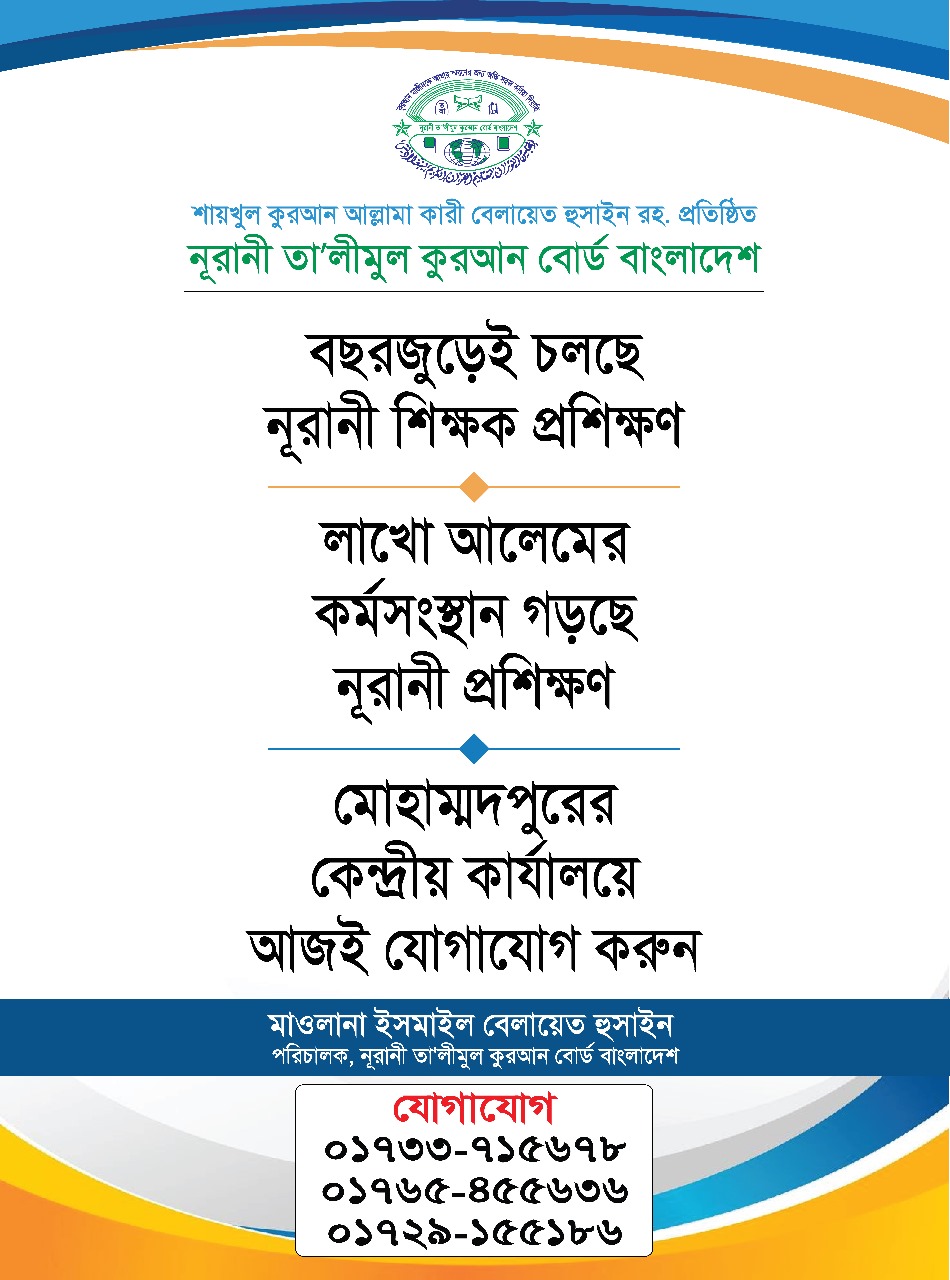
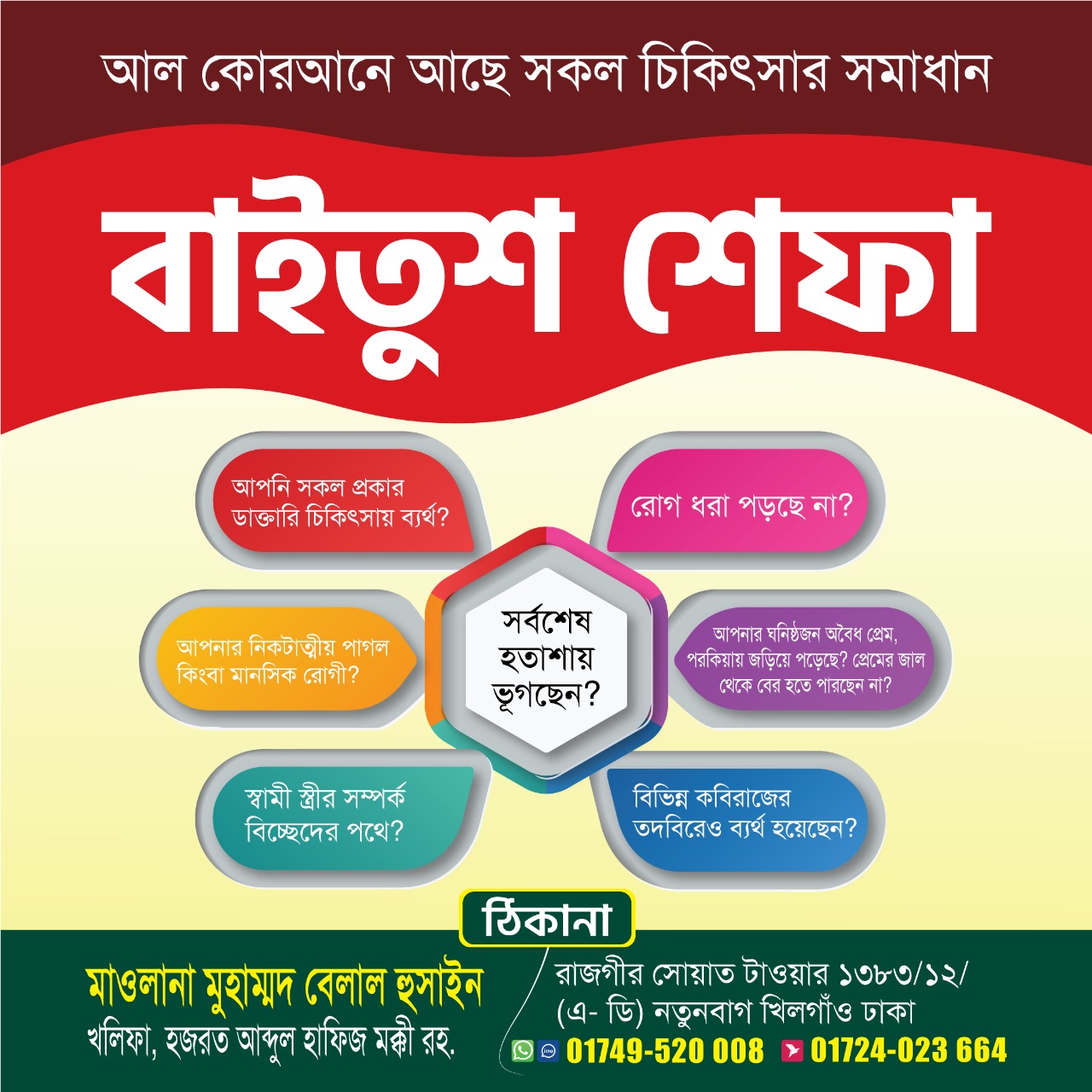
_medium_1754365057.jpg)