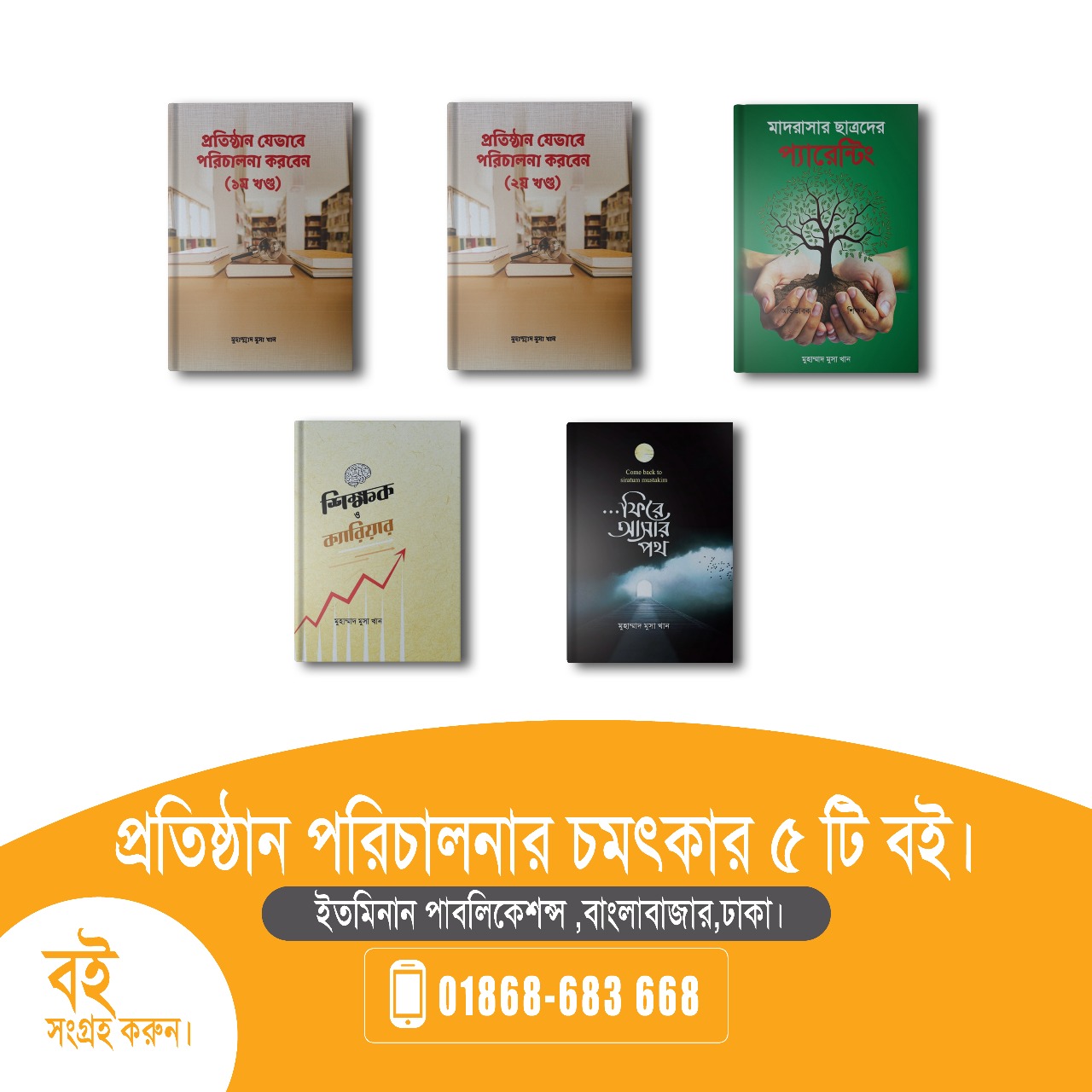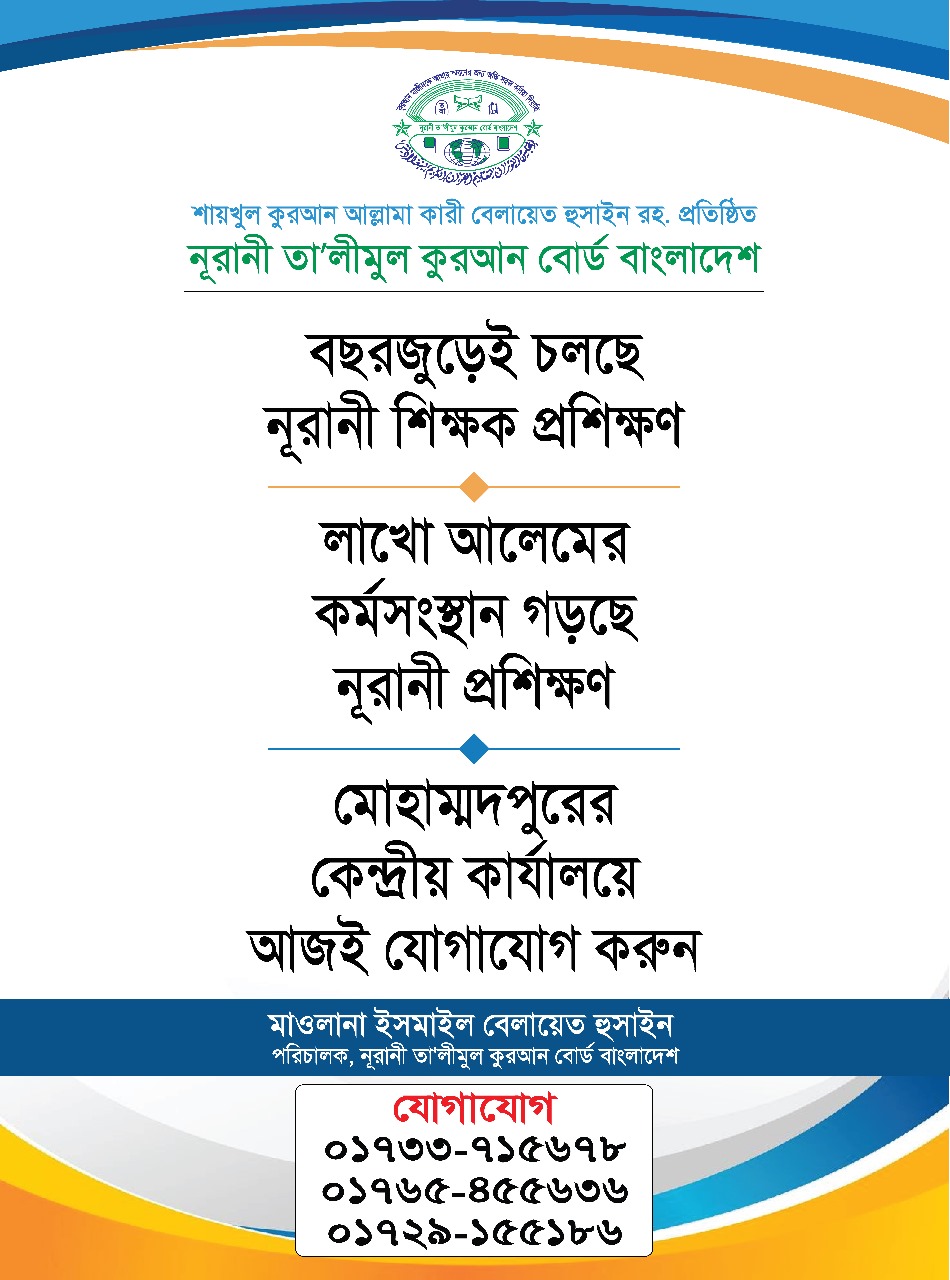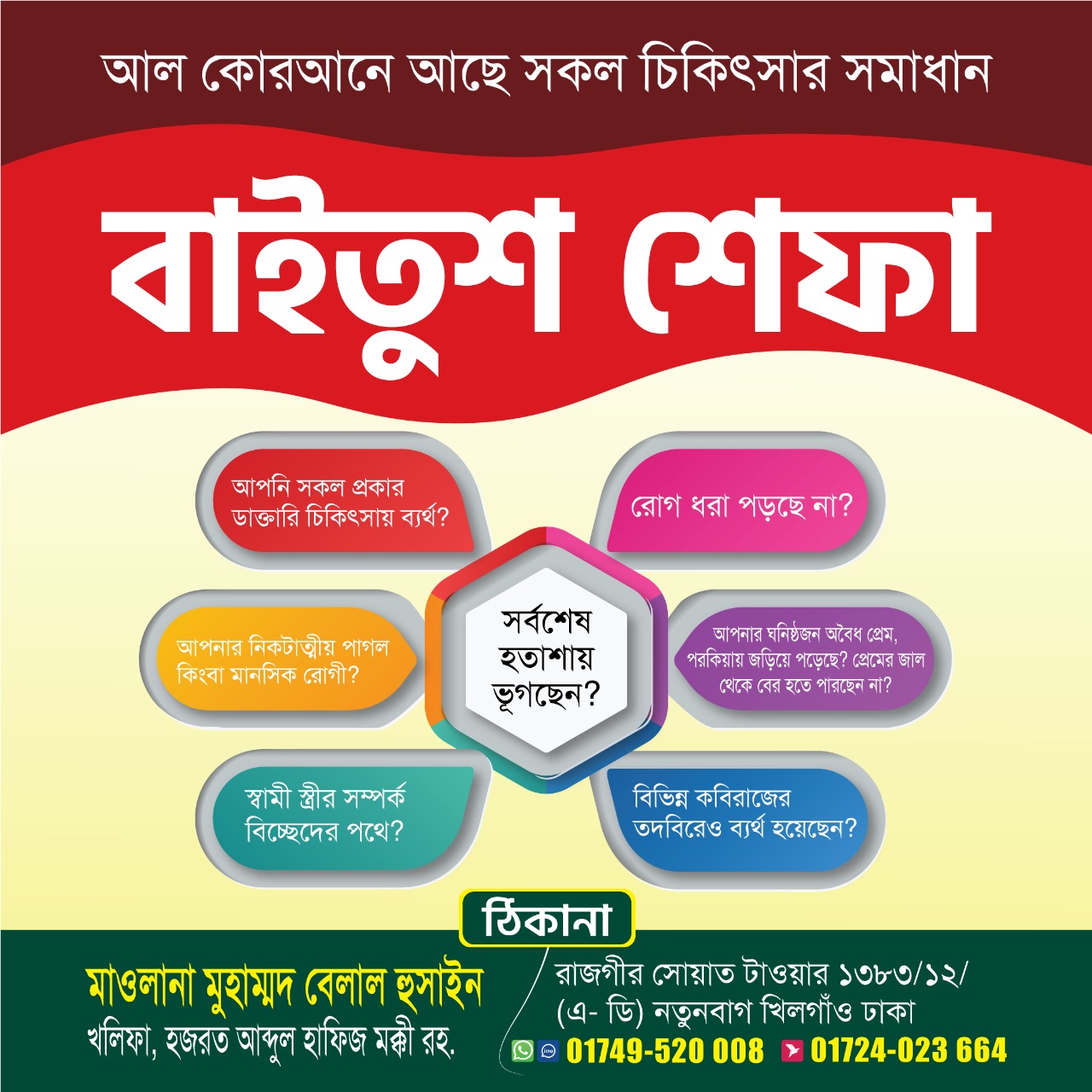মুফতি মুহাম্মাদ শোয়াইব
‘বাই বিল ওয়াফা’ শব্দটি আরবি। এর দ্বারা বিশেষ একটি লেনদেনকে বোঝানো হয়। ‘বাই বিল ওয়াফা’ বলা হয় কোনো জিনিস এ শর্তে বিক্রি করা যে, নির্ধারিত কিছুদিন পর ওই জিনিসটি বিক্রিত মূল্যে ফেরত দেবে। কারও টাকা প্রয়োজন হলে সে তার মালিকানাধীন কোনো সম্পদ বা পণ্য এ শর্তে বিক্রি করে দেয়, যে মূল্যে বিক্রি করেছে পরবর্তী সময় সেই মূল্য পরিশোধ করে দিলে ক্রেতা তার পণ্য ফেরত দেবে। এ শর্তটি আকদ চলাকালীন যুক্ত করা হতে পারে কিংবা আকদ সম্পন্ন করার আগেই যুক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন কারও ১ লাখ টাকার প্রয়োজন। কোনো সম্পদশালীর সঙ্গে সে এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, সে তার একটি মালিকানাধীন জমি ১ লাখ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করবে। শর্ত হলো, যখন বিক্রেতা ১ লাখ টাকা ফেরত দেবে, তখন ক্রেতা তার জমি ফেরত দেবে। এ ধরনের চুক্তিকে বাই বিল ওয়াফা বলা হয়। কারণ এখানে প্রত্যেকে অপরের প্রতি যে চুক্তি ছিল, তা পূরণ করে থাকে। (মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ, ধারা-১১৮)।
এর আরও কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন বাইউল আমানাহ, বাইউল মুআমালা, বাইউল ইতায়াহ।
এ বেচাকেনাটি হানাফি ওলামায়ে কেরামের কাছে সর্বপ্রথম হিজরির পঞ্চম শতাব্দী তথা ঈসায়ি একাদশ শতকে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের প্রয়োজনেই এ ধরনের একটি বেচাকেনার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কারণ বিভিন্ন সময় মানুষের ঋণ নেয়ার প্রয়োজন হয়। আবার ঋণদাতাও উপকার লাভ ছাড়া সাধারণত ঋণ দিতে প্রস্তুত থাকে না। তাই প্রাচীনকাল থেকেই বন্ধকের মাধ্যমে ঋণ নেয়ার প্রচলন ছিল। অর্থাৎ কোনো কিছু বন্ধক রেখে ঋণ নেয়া হতো। এতে ঋণদাতা বন্ধকি দ্রব্য দ্বারা উপকৃত হতে পারত। আবার যখন ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা ফেরত দিত, তখন ঋণদাতাও বন্ধকি দ্রব্যটি ফেরত দিয়ে দিত। কিন্তু সমস্যা হলো, ঋণদাতার জন্য বন্ধকি বস্তু থেকে উপকার হাসিল করা জায়েজ নয়। ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা নেয়াও জায়েজ নয়। সুতরাং ঋণ দিয়ে কিছু মুনাফাও যাতে কামানো যায় আবার এ মুনাফা যাতে ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধও না হয়- এ দ্বিমুখী চিন্তা থেকে উৎপত্তি হয় বাই বিল ওয়াফা, যা সুদ গ্রহণের একটি সুস্পষ্ট কৌশল। বাই বিল ওয়াফাতে বন্ধক রেখে ঋণ দেয়ার পরিবর্তে বন্ধকি বস্তুটি ফেরত দেয়ার শর্তে ঋণদাতার কাছে বিক্রি করে দেয়। এতে ঋণদাতা বন্ধকি বস্তু দিয়ে উপকৃত হতে পারে। সে তা ভোগ করতে পারে। অন্যদিকে ঋণগ্রহীতারও ঋণগ্রহণের হাজত পূর্ণ হয়। এরপর পূর্ব ওয়াদা অনুযায়ী অর্থ ফেরত দিয়ে তার পণ্য ফেরত নেয়ারও সুযোগ থাকে।
হানাফি ওলামায়ে কেরামের একটি অংশ এ বেচাকেনাকে প্রয়োজনের কারণে শর্তসাপেক্ষে জায়েজ বলেন। অন্য একটি শ্রেণী এ বেচাকেনাকে নাজায়েজ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ এতে ক্রয়-বিক্রয়ে চুক্তির চাহিদাবিরোধী শর্ত পাওয়া যায়। চুক্তির চাহিদা হলো বস্তুটি বিক্রেতা থেকে ক্রেতার মালিকানায় সম্পূর্ণরূপে চলে আসা এবং ক্রেতার টাকা বিক্রেতার মালিকানায় পূর্ণরূপে চলে যাওয়া। কিন্তু নির্ধারিত কিছুদিন পর বিক্রীত বস্তুটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে, এমন শর্ত করলে মালিকানা সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের পর যদি বস্তুটি ফেরত নেয়া বা দেয়ার ওয়াদা করে, তাহলে ওই চুক্তিটি জায়েজ হবে এবং এ ওয়াদা পূর্ণ করা জরুরি। (আদ-দুররুল মুখতার : ৭/৫৪৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ৩/৩, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া : ৬/২৮৬, আহসানুল ফাতাওয়া : ৬/৫০৭)।
অনেক ওলামায়ে কেরামই বাই বিল ওয়াফাকে রহন বা বন্ধক নামে আখ্যায়িত করেছেন। তারা মনে করেন, এখানে বাই শব্দ উল্লেখ করলেও প্রকারান্তরে এটি রহন বা বন্ধক। বন্ধক রাখা হয় ঋণ আদায়ের নিশ্চয়তাস্বরূপ। রহন বা বন্ধক বলা হয় সেই সম্পদকে, যা ঋণের পরিবর্তে গ্যারান্টিস্বরূপ রাখা হয়, যাতে ঋণ উসুল করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে বা ঋণ উসুল করা অসম্ভব হয়ে পড়লে বন্ধক রাখা সম্পদ থেকে পাওনা উসুল করে নিতে পারে। ঋণ আদায় না করলে বা গড়িমসি করলে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধক রাখা বস্তুটি বিক্রি করে সে তার পাওনা রেখে দিয়ে বাকি সম্পদ বন্ধকদাতা তথা মালিককে ফেরত দিতে পারে। কিন্তু পরবর্তী সময় বন্ধককে সুদ খাওয়ার একটি কৌশল হিসেবে আবিষ্কার করা হয়। ঋণ দিয়ে কিছু উপকার হাসিল করার ‘বৈধ’ পন্থা হিসেবে বন্ধককে গ্রহণ করা হয়। অথচ বন্ধকি জিনিস থেকে বন্ধকগ্রহীতার কোনো ধরনের ফায়দা উপভোগ করা সুদের অন্তর্ভুক্ত, যা হারাম। এমনকি বন্ধকদাতা এর অনুমতি দিলেও পারবেন না। তাই বন্ধকি জিনিস থেকে উৎপন্ন উপকার ভোগ করা হালাল হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে : ৬/১৪৬)।
ইবনে শিরিন (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক লোক ইবনে মাসউদ (রা.) এর কাছে জিজ্ঞেস করল, এক ব্যক্তি আমার কাছে একটি ঘোড়া বন্ধক রেখেছে, তা আমি আরোহণের কাজে ব্যবহার করেছি। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, তুমি আরোহণের মাধ্যমে এর থেকে যে উপকার লাভ করেছ, তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ১৫০৭১)।
বিখ্যাত তাবেঈ ইমাম কাজী শুরাইহ (রহ.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সুদ পান করা কীভাবে হয়ে থাকে? তিনি বলেন, বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকি গাভীর দুধ পান করা সুদের অন্তর্ভুক্ত। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ১৫০৬৯)।
বন্ধকি জিনিস বন্ধকগ্রহীতার কাছে আমানতস্বরূপ। পবিত্র কোরআনেও এর নির্দেশ রয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, ‘আর যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোনো লেখক না পাও, তাহলে হস্তান্তরযোগ্য বস্তু বন্ধক রাখবে। আর যদি তোমরা একে অপরকে বিশ্বস্ত মনে করো, তবে যাকে বিশ্বস্ত মনে করা হয়, সে যেন স্বীয় আমানত আদায় করে এবং নিজ রব আল্লাহকে ভয় করে।’ (সূরা বাকারা : ২৮৩)।
বর্তমানে বন্ধকি বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার নব কৌশল হিসেবে বাই বিল ওয়াফাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্য ভাষায় বলা যায়, সুদ খাওয়ার নতুন কৌশল হলো বাই বিল ওয়াফা। বাই শব্দটি বলা হলেও এটি মূলত ঋণ দিয়ে বন্ধকি বস্তু দ্বারা উপকার হাসিল করার একটি কৌশল মাত্র। ওমর (রা.) বলেন, বাই বিল ওয়াফা প্রচলনগত দিক থেকে বন্ধক। চুক্তির সময় ‘বাই’ শব্দ উল্লেখ করলেও এটি রহন। কেননা চুক্তিতে শব্দের গ্রহণযোগ্যতা নেই, উদ্দেশ্যের গ্রহণযোগ্যতা। আর এখানে ‘বাই’ শব্দ দিয়ে প্রচলনগত দিক থেকে ‘রহন’ উদ্দেশ্য নেয়ার বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট। (কামুসুল হুকুকিল ইসলামিয়া : ৬/১২৭, জামেউল ফুসুলাইন-মাহমুদ ইবনে ইসরাইল কৃত : ১০/২৩৪-২৩৫)।
সুদের এ কৌশল থেকে বাঁচার জন্য ওলামায়ে কেরাম বাই বিল ওয়াফা না করে তার পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি ইজারা চুক্তি করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যত দিন পর্যন্ত ঋণের টাকা শোধ না হয়, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে গ্যারান্টিস্বরূপ পাওয়া বস্তুটিকে ইজারা পদ্ধতিতে ভোগ করবে এবং তার ন্যায্য ভাড়াও মালিককে আদায় করবে। এক্ষেত্রে ঋণ ও ইজারা চুক্তি দুইটি ভিন্ন হতে হবে। দুইটি চুক্তি মিলিয়ে একটি অপরটির ওপর শর্তযুক্ত হতে পারবে না। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : ৫/৪৬৫, ইমদাদুল আহকাম : ৩/৫১৮)। স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদে যে কোনো জিনিস ইজারা তথা ভাড়া দেয়া বৈধ। ভাড়া নিয়ে এমন যে কোনো বৈধ কাজে লাগানো জায়েজ হবে, যার কারণে ভাড়া নেয়া বস্তুটির উল্লেখযোগ্য ক্ষতি না হয়।
লেখক : সম্পাদক, মাসিক আরবি ম্যাগাজিন, ‘আলহেরা’
ইজারার মাধ্যমে বিনিয়োগের হুকুম ও নীতিমালা