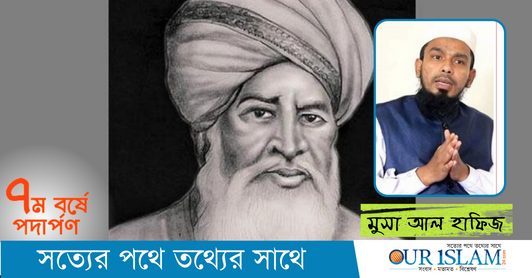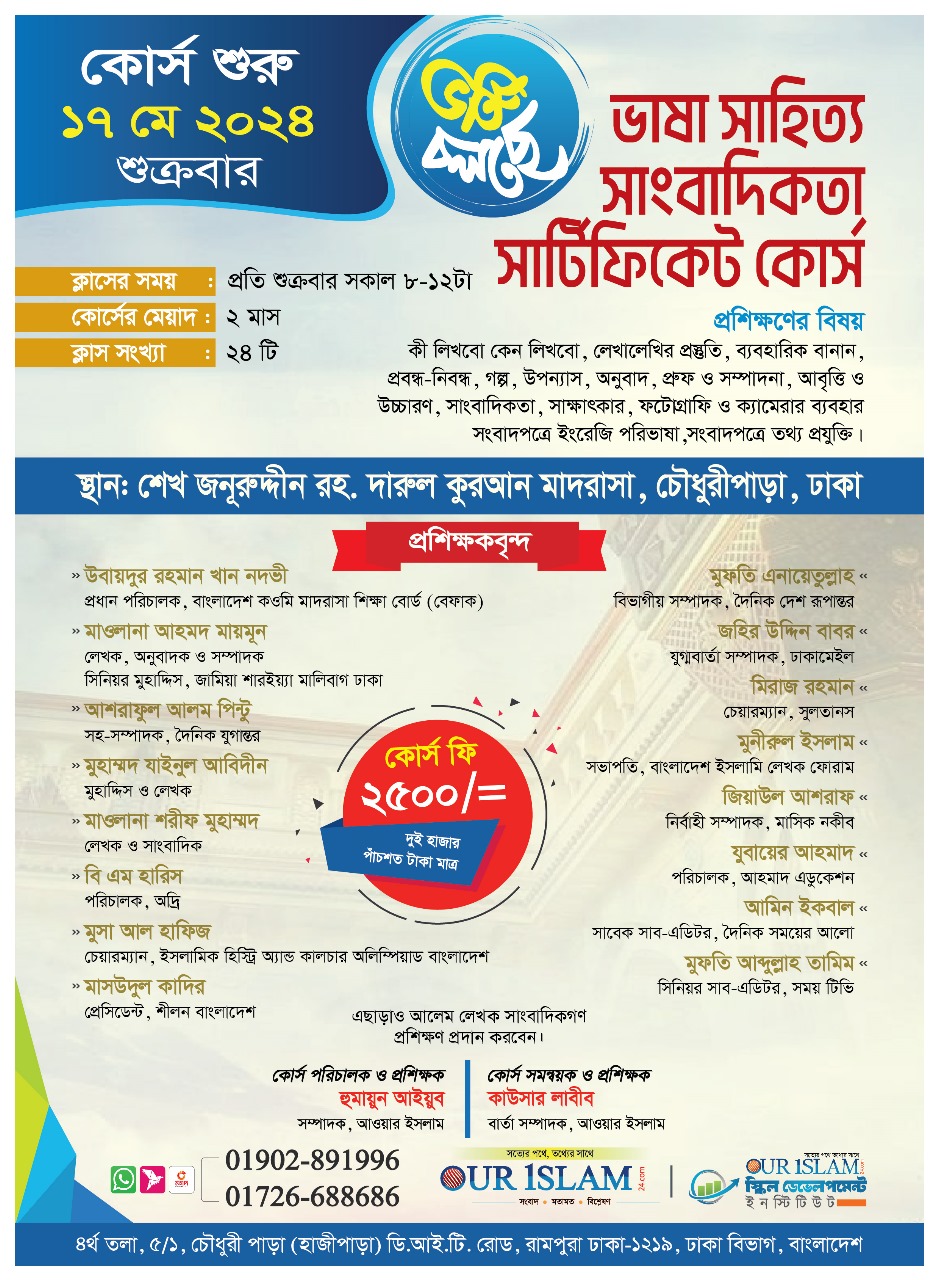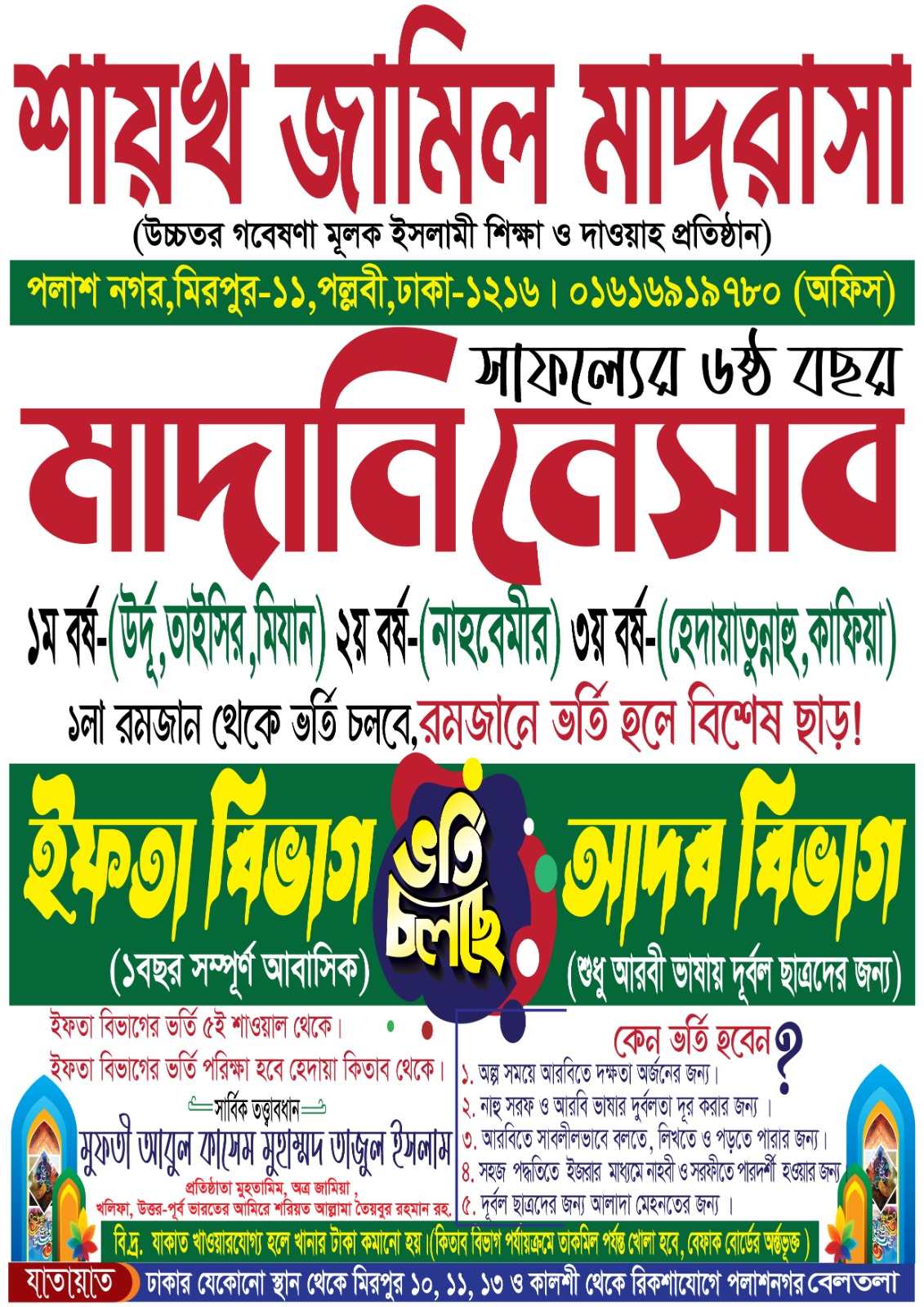মুসা আল হাফিজ
বলা হয়, তথ্য নিজেই কথা বলে। একমত নই। তথ্যরা তখনই কথা বলে, যখন ঐতিহাসিক তাকে মঞ্চে দাঁড় করান। ঐতিহাসিক আপন নির্বাচন ও বিন্যাসে তথ্যদের কাউকে বলার জায়গায় রাখেন, কাউকে চুপ করিয়ে দেন। বিভিন্ন ক্রম ও প্রসঙ্গে তথ্যদের নির্ণয় ও বিবেচনা করে তাদের আমন্ত্রণ করেন। ফলে তার হাতে ইতিহাস হয় ভাঙা টুকরো দিয়ে জোড়া লাগানো এক স্থাপত্য, যার অনেক টুকরো হারিয়ে গেছে বা ফেলে দেয়া হয়েছে। যাকে নির্মাতা রঙ দিয়েছেন আপন মনের ধরন ও গড়নের হাত দিয়ে।
প্রশ্ন হলো, কে কাকে ফেলে দিচ্ছেন বা কোনো বিষয়ের হারিয়ে যাওয়াই প্রত্যাশা করছেন? কে কাকে দিচ্ছেন কোন রঙ?
ধরেন উইলিয়াম উইলসন হান্টারের কথা। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের অফিসার। ইংরেজ স্বার্থের দিকে নজর দিয়ে তিনি যখন ফরায়েজী আন্দোলনকে দেখলেন ও দেখালেন, সেখানে তথ্যগুলো এমনভাবে এলো, যা প্রমাণ করতে চায় ফরায়েজী আন্দোলন একটি ষড়যন্ত্র, দেশদ্রোহিতা!
হান্টার লুকাতে পারেননি অভিপ্রায়। তার ভাষ্যে ফরায়েজীরা ‘বিপজ্জনক’ তারা ‘গ্রাম পুড়িয়েছে’, ‘প্রজাদের হত্যা করেছে’ সর্বত্র বিস্তার করেছে ‘ষড়যন্ত্রের জাল’, তাদের প্রত্যেকেই এমন, যারা ‘ব্যক্তিগত স্বার্থকে গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থ বলে বিবেচনা করে থাকে’, তাদের ‘অশুভ প্রভাব ব্যাপক আকার ধারণ করেছে’, তারা ‘বিদ্রোহী’, ‘ওয়াহাবি’। এরা রাষ্ট্রের ভেতরে ‘বিদ্রোহী কলোনি’ গড়ে তুলেছে, এমনকি তাদের আছে ‘অজস্র রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য’। হান্টারের বয়ান শোনা যাক : ‘বাংলার মুসলমানরা আবার বিচিত্র ধরন নিয়েছে, গ্রাম পুড়িয়েছে, আমাদের প্রজাদের মেরে ফেলেছে এবং আমাদের সীমান্তের ওপারে মাসের পর মাস ধরে গড়ে ওঠা শত্রু-বসতির লোক নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলার ভেতর থেকে। বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক মোকদ্দমার বিচার থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের প্রদেশগুলোর সর্বত্র বিস্তারিত হয়েছে এক ষড়যন্ত্রের জাল।’
‘গাঙ্গের ব-দ্বীপ এলাকার ধর্মান্ধ মুসলমানরা নিজেদের ওয়াহাবি না বলে ফরায়েজী অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের অনাবশ্যকীয় আচারানুষ্ঠানাদি বর্জনকারী হিসেবে পরিচিত করে। কলকাতার পূর্ব দিকের জেলাগুলোতে এদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়।
১৮৪৩ সালে এই সম্প্রদায়টি এতদূর বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যে, তাদের সম্পর্কে তদন্তের জন্য সরকারকে বিশেষ তথ্যানুসন্ধান কমিশন নিয়োগ করতে হয়। বাংলার পুলিশপ্রধানের প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হয়, ‘মাত্র একজন প্রচারক (হাজী শরীয়তুল্লাহ) প্রায় আশি হাজার অনুগামীর এক বিরাট দল গড়ে তুলেছে এবং তারা প্রত্যেকেই যার যার নিজস্ব স্বার্থকে গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থ বলে বিবেচনা করে থাকে।’...
‘এসব প্রচারকের অশুভ প্রভাব ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।... এরা এমন ধর্মান্ধদের তহবিলে দান করেছিল- দলের পর দল সংগ্রহ করে ধর্মান্ধ শিবিরে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছিল। দেশের সর্বত্র মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে তারা গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল অজস্র রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য, পাটনায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রচার কেন্দ্র এবং সারা বাংলার আনাচে কানাচে প্রচারকদের আনাগোনা ছাড়াও জনগণের মধ্যে রাজদ্রোহমূলক কাজে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য ওয়াহাবিরা সংগঠন গড়ে তুলেছে। এভাবে পল্লী বাংলার বিভিন্ন স্থানে একধরনের বিদ্রোহী কলোনি গড়ে উঠেছে।’
হান্টারের সিদ্ধান্ত পূর্বস্থির। এরা শত্রু, হীন। ব্রিটিশ শাসনই মহান, ন্যায্য। অতএব এদের ব্যক্ত করতে তার প্রমাণসূত্র সরকারি গোয়েন্দা রিপোর্ট, মামলার নথি, পুলিশপ্রধানের ভাষ্য ইত্যাদি।
তিনি নিয়োজিত ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তদন্ত রিপোর্ট তৈরির কাজে। সেই পক্ষপাত, ব্রিটিশ স্বার্থের দেখভাল, শোষক জমিদার ও তাদের লাঠিয়ালদের জনগণ বলে দেখা আর জনগণকে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে দেখার জায়গা থেকে তিনি তথ্য সরবরাহ করেছেন।
এর মধ্যে কি আমরা ফরায়েজী আন্দোলনকে পাই? পাই বটে! হান্টারের এ অবস্থানকে মাথায় রেখে আমরা যখন তাকে পড়ি, বুঝি ফরায়েজী আন্দোলন ঔপনিবেশিক শক্তির নাগপাশকে কিভাবে শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছিল এবং কত গভীরভাবে গণমুক্তির আকাক্সক্ষা ও সাধনাকে সংগঠিত করছিল।
এর প্রভাব ও আবেদন, বিস্তার ও গভীরতা এবং সামাজিক সক্ষমতা ও সাংগঠনিকতা এর মধ্যে অস্পষ্ট নয়। যেখানে ‘জমির খাজনা পরিশোধ করতে অসমর্থ কৃষকরাও জিহাদের জন্য নিয়মিত অর্থ’ প্রদান করত স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ছিল সুদূরপ্রসারী- গণজীবনের সংস্কারের পাশাপাশি জাতীয় মুক্তির অভিসারী এবং সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত, লড়াকু ও আত্মত্যাগী; হান্টারের বয়ানে এটি লুকানো থাকছে না। তিনি লিখেন,
‘পাঞ্জাবের উত্তরে অবস্থিত জনহীন পর্বতরাজির সাথে উষ্ণমণ্ডলীয় গঙ্গা অববাহিকার জলাভূমি অঞ্চলের (বাংলার) যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে রাজদ্রোহীদের নিরবচ্ছিন্ন সমাবেশের মাধ্যমে। সুসংগঠিত প্রচেষ্টায় তারা ব-দ্বীপ অঞ্চল (বাংলা) থেকে অর্থ ও লোক সংগ্রহ করে এবং দুই হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্রোহী শিবিরে তা চালান করে দেয়।
বাংলার এমন কোনো জনপদ ছিল না, যেখানকার মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ আহমদের সংস্কারের বাণী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। প্রতিটি ধার্মিক পরিবারের যুবকরা সীমান্তে গিয়ে জিহাদ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে একদিন তারা হঠাৎ করে সীমান্তের মুজাহিদ কাফেলায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ত। জমির খাজনা পরিশোধ করতে অসমর্থ কৃষকরাও জিহাদের জন্য নিয়মিত অর্থ প্রদান করতে কুণ্ঠিত হতো না।’
হান্টারের বয়ান থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমরা বাংলার তৃণমূলের মুক্তিকামী জনতার একটি আত্মজ সংগ্রামের সাথেই পরিচিত হলাম। যা বাংলার গণজীবনকে করেছিল মথিত, আন্দোলিত ও ব্রিটিশ দুঃশাসনকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল তীব্রভাবে।
এই যখন বাস্তবতা, তখন নিন্দা করতে চাইলেও এর তলা থেকে বেরিয়ে আসে বাস্তবতা। জেমস ওয়াইজ অতএব হাজী শরীয়তুল্লাহকে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে উদাসীন ও অসচেতন বাংলার মুসলমান কৃষকদের আত্মসচেতন ও উজ্জীবিত করার কাজে নিয়োজিত একজন একনিষ্ঠ ও সহানুভূতিশীল প্রচারকরূপে স্বীকার করে নেন।
ফরিদপুরের তখনকার মাদারীপুর মহকুমার শ্যামাইল গ্রামের তালুকদার পরিবারে ১৭৮১ জন্মগ্রহণকারী হাজী শরীয়তুল্লাহর নামানুসারে নামকরণ হয় যে শরীয়তপুর জেলার, সেটিই কেবল তার লড়াই-সংগ্রামের কেন্দ্র ছিল না; বরং ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ (বর্তমান বরিশাল), ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা), চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলাগুলোতে এবং আসাম প্রদেশে ছিল এর প্রবল বিস্তার।
যেসব এলাকা নব্য হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারে রক্তাক্ত ছিল এবং কৃষকদের ওপর অত্যাচার যেখানেই শিলাচাপা অবস্থা তৈরি করছিল, সেখানেই ফরায়েজী আন্দোলন মানুষের সংগ্রাম ও প্রতিরোধের অবলম্বন হয়ে ওঠে।
১৭৯৯ সালে, ১৮ বছর বয়সে শরীয়তুল্লাহ যখন মক্কা যান, দেখে যান, পলাশীর প্রহসনের পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকদের তুলাদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে এ দেশের সর্বত্র কী বিপদের রাত ডেকে এনেছে! যে দেশে মুসলিম শাসনের ৫০০ বছরে কোনো দুর্ভিক্ষ হয়নি, সেখানে ব্রিটিশ তাদের ও এদেশীয় শিখণ্ডিদের শোষণ-লুণ্ঠনের ফলে পলাশী বিপর্যয়ের মাত্র দুই দশকের মধ্যেই ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে কুকুর-বিড়ালের মতো প্রাণ হারাল এ দেশের লক্ষকোটি বনি আদম। এ দুর্ভিক্ষ এখানকার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের প্রাণ কেড়ে নেয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষের মধ্যেও করের তীব্রতা বেড়েছে!
তার মনে গেঁথে গেল স্বাধীনতা হরণকারীদের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত বাংলার কৃষকের মুখ আর ধর্মের নামে ধর্মবর্জিত কুসংস্কারে থইথই করা সামাজিক বাস্তবতা। যে মুসলিমরা একদা সেনাবাহিনীতে, জমিদারিতে, ব্যবসায়, শিল্পে, কৃষিতে সমৃদ্ধ জীবনের নিশ্চয়তার মধ্যে ছিল, তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে সব সুবিধা থেকে, কেবল সেনাবাহিনী থেকে ৮০ হাজার মুসলমানকে উচ্ছেদ করা হয় পলাশীর পতনের ১০ বছরের মাথায়। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মুসলিমদের উচ্ছেদ করে জমিদারি থেকে।
তাদেরই সাবেক প্রজা হিন্দুদের নতুন এক জমিদার শ্রেণী গড়ে তোলে, হঠাৎ পাওয়া ক্ষমতার জোর দেখানো এবং করের নামে দস্যুতা, ধারাবাহিক অত্যাচার ও প্রজাপীড়নই ছিল তাদের জমিদারির মাতৃভাষা! জমিদার ও গোমস্তারা চাল ব্যবসায়ীদের বাধ্য করে সবচেয়ে কম দামে চাল বিক্রি করতে এবং তার পর তারা তা সংগ্রহ করে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে।
গোমস্তাদের সাহায্যে তারা তাঁতিদের অর্ধেক মূল্যে ভাগ বসায়। প্রজাদের ওপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তা ও কর্মচারীদের লুণ্ঠন ও শোষণ ছিল চরম মাত্রার। এটি নীচুতার চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। ঔপনিবেশিকতার সেবক অনেক ঐতিহাসিকও একে উল্লেখ করেছেন দুঃখের সাথে। ঐতিহাসিক জেমস মিল জানান, কোম্পানির কর্মচারীদের আচরণ ‘ক্ষমতা ও স্বার্থের সবচেয়ে লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, যা ন্যায়বিচার এমনকি লজ্জার সব বোধকে শেষ করে দেয়’।
এ পরিস্থিতিতে কিছু দিন আগেও যে মুসলমানরা ছিল সমৃদ্ধ, তারা হয়ে চলে নিঃস্ব। নিজেদের অর্থনীতি থেকে তারা উচ্ছেদ হয়েছে, হারিয়েছে সংস্কৃতি, সম্মান, নিশ্চয়তা ও অবস্থান। কলোনি শাসক এবং তাদের সহযোগী নীলকর, হিন্দু জমিদার, মাড়োয়ারি ও গোমস্তারা কৃষি-শিল্প, হাটবাজার, নদী, বন্দর কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে মুসলিম তৃণমূলকে নামিয়ে দিয়েছে ক্রীতদাসের স্তরে।
হিন্দু ধর্মাচারে অংশগ্রহণ, পীরদের নামে মান্নত, গাজী ও কালুর দুর্গা তৈরি, বারো মাসে বারো পূজা, দশ হরা রথযাত্রা, চড়ক পূজা, পীরের নামে জনে জনে পূজা দেয়া, পাঁচ পীরের নামে মোকাম উঠানো, বাড়ির চার দিকে কলাগাছ গাড়া, ধুতি পরিধান ইত্যাদি মুসলিম গণজীবনের গভীরে ঢুকে পড়ে।
প্রতিবেশী সমাজের প্রভাবে বর্ণ প্রথা সৈয়দ, শেখ, পাঠান ও মোল্লা অভিধাধারীদের উচ্চশ্রেণী করে তুলেছিল। খন্দকার, চৌধুরী, কাজী প্রভৃতিকে মধ্যবর্তী অবস্থান দিচ্ছিল এবং তাঁতি, খনক, জেলে, তেলী, কাহার বা চাকর (পালকী বাহক ও পাখা চালক) ইত্যাদিকে নিম্নতম জায়গায় নিয়ে যায়। পেশাগত বর্ণবাদ বংশীয় বর্ণবাদের সাথে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলে!
মক্কায় একটানা ২০ বছরে গভীর অধ্যয়ন ও সাধনা সম্পন্ন করে শরীয়তুল্লাহ ১৮১৮ সালে যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন, সাবেক অন্ধকার ও দুর্গত দশা আরো ঘনকালো হয়েছে। রাজনৈতিক বিপন্নতার পাশাপাশি ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এই জনগোষ্ঠী আত্মবোধ ও স্বকীয় সত্তা হারিয়েছে আগের চেয়ে বেশি।
আরবে তখন বইছে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব (১৮০৩-৯২) পরিচালিত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ঝড়। শিরক, বিদআত প্রভৃতি অবাঞ্ছিত কুসংস্কারের উচ্ছেদে এ আন্দোলনের প্রেরণাকে আত্তীকরণ করেন শরীয়তুল্লাহ। তবে এর সাথে তার ভিন্নতা ছিল গভীর। ওয়াহাবি আন্দোলন বলে বিখ্যাত এ সংস্কারপ্রয়াসের বিভিন্ন আকিদাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি, মাজহাব বিরোধিতাকে যেমন স্বীকৃতি দেননি, তেমনি বাংলার মুসলমানদের জন্য হাম্বলি মাজহাব ও সালাফি আকিদাকে অবলম্বনের কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।
ফলে ওয়াহাবি ধারার সাথে তার দূরত্ব ছিল স্পষ্ট। তিনি প্রধানত প্রভাবিত ছিলেন প্রধানত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবীর (১৭০৩-১৭৭৯) চিন্তা ও দর্শনে। তার ছেলে আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবী (১৭৪৬-১৮২৩) ঘোষিত দারুল হারব বা শত্রুকবলিত রাষ্ট্রতত্ত্বকে তিনি অবলম্বন করেন এবং বাংলাভূমিকে আশ্রয় করে ব্রিটিশশাসিত উপমহাদেশের মুক্তির উদ্দীপনা ও আয়োজন সংগঠিত করেন। সায়্যিদ আহমদ শহীদের (১৭৮৬-১৮৩১) সংস্কারপ্রয়াস ও মুক্তিসংগ্রাম তার সামনে ছিল তাজা নমুনা। সেই ধারাবাহিকতার সফরসঙ্গী হয়েছিলেন তিনি।
কিন্তু তিনি বিগত প্রচেষ্টাগুলোর ফলাফল নিরীক্ষণ করেছিলেন। বিশেষত এ অঞ্চলে মজনু শাহ বোরহানের (মৃত্যু : ১৭৮৭) নেতৃত্বে মুক্তির জন্য পরিচালিত গেরিলা তৎপরতা, তিতুমীরের (১৭৮২-১৮৩১) কৃষক সংগ্রাম ইত্যাদির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলের ওপর ছিল তার অন্তর্দৃষ্টি। ফরায়েজী আন্দোলনকে তিনি ইতঃপূর্বেকার মুক্তি ও সংস্কার প্রয়াসগুলোর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিস্থাপন করলেন। তিনি একে এমন এক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক আবহে বিকশিত করলেন, যার আছে গণলগ্নতার গভীর ও ব্যাপক জাতীয় উপযোগ।
আরবি ফারাইজ হচ্ছে ফরিজাতুনের বহুবচন। ফারিজা বা ফরজ মানে হচ্ছে অবশ্য পালনীয়। ফরায়েজী আন্দোলন মূলত ইসলামের অবশ্যপালনীয় কর্তব্যে মুসলিমদের অনুশীলন নিশ্চিত করতে জোর দিচ্ছিল।
প্রধান কর্তব্য হলো- কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত। প্রধান বিষয়গুলো উপেক্ষা করে ইসলামে অস্বীকৃত কিংবা ইসলামবহির্ভূত বিষয়াবলিকে ইসলাম হিসেবে পালনের প্রথা পরিহারে উদ্বুদ্ধ করেন ফরায়েজীরা। ইসলামের সত্যিকার অনুশীলনে ফিরে যাওয়া এবং মুসলিম সমাজের পরিশুদ্ধি ছিল তাদের প্রয়াসের মর্মমূলে। তাওহিদের বিশুদ্ধতার প্রতিষ্ঠাদান, সুন্নাহর অনুসরণ ও প্রসারের নিশ্চয়তা বিধান, তাওবার প্রক্রিয়ায় পাপ থেকে ফিরে এসে ধর্মনৈতিক শুদ্ধাচারে কল্যাণী জীবন-অনুশীলন ইত্যাদিকে এ আন্দোলন গুরুত্ব দেয়। অন্যান্য মুসলমানের চেয়ে কড়াকড়ি নৈতিকতা অবলম্বন করতেন তারা।
তাওহিদের সাথে সঙ্গতিশীল নয়, এমন বিষয়াবলি পরিহারে মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করেন। এ আন্দোলন মুসলিম সমাজে বর্ণবাদকে রুখে দাঁড়ায়, অনুসারীদের বংশীয় পদবি ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। খাবার-দাবার, পোশাকাদি, আচার-আচরণকে ইসলামের বিধান ও সংস্কৃতির অনুগত করতে সচেষ্ট হয়। অতএব ধুতি নয়, লুঙ্গি-পাজামা, বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব নয়, মানুষে মানুষে সমতা, কোনো সৃষ্টির সমীপে পূজা নয়, নিরঙ্কুশ তাওহিদ, এমনকি গরুর গোশত নিষিদ্ধ হতে পারে না...
বিকাশের ধারায় এ আন্দোলন বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সাথে হয় অবিচ্ছেদ্য। ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদে উদ্বুদ্ধ করার পথে মুসলিম কৃষক শ্রেণীর ধর্মীয় জীবনাচারে চেপে বসা অনৈসলামিক বিশ্বাস ও আচারকে সে সংশোধনের প্রয়াস জারি রাখে।
এ প্রক্রিয়ায় এ আন্দোলনের সূচনা হলেও অচিরেই বৃহত্তর আরেক রণাঙ্গনে তাকে অবতীর্ণ হতে হয়, যা প্রস্তুত ছিল আগে থেকেই। ব্রিটিশ শোষণের অক্টোপাসী বেষ্টনী গণজীবনকে চেপে ধরেছিল সব দিক থেকে। নবোত্থিত জমিদার শ্রেণী মূলত ছিল হিন্দু। যাদের প্রধান অংশ ছিল ঘোরতর সাম্প্রদায়িক ও মুসলিম নিপীড়নে উৎসাহী। তাদের অনেকেই ছিল হিংস্র, দেবী সিংহের মতো ডাকাত; জমিদার হয়ে যিনি রাজা-মহারাজা উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য হয়ে উঠেন জীবন্ত যমদূত!
জমিদাররা কালীপূজা, দুর্গাপূজা, রথযাত্রা ইত্যাদির জন্য কর নিত- কী হিন্দু থেকে, কী মুসলিম থেকে। জমিদার সন্তানের অন্নপ্রাশন, বিয়ে বা ‘জামাই খরচা’ ইত্যাদির নামে লেগেই থাকত বাড়তি খাজনার দাবি। ১৮৭২ সালে ফরিদপুরে কর্মরত ম্যাজিস্ট্রেটের এক তদন্তে দেখা যায়, কৃষকদের ওপর জমিদারদের আরোপিত অবৈধ করের সংখ্যা ২৩-এর কম নয়। কোনো মুসলিম দাড়ি রাখলেও কর দিতে হতো। নিজেদের এলাকায় তারা কোরবানি বন্ধ করে, আজান নিষিদ্ধ করে, গরু জবাই ও গোশত খাওয়ার ওপর জারি করে নিষেধাজ্ঞা। যখন তখন তাদের নিপীড়ন নেমে আসত নিঃস্ব প্রজার ওপর।
তারা লাঠিয়াল বাহিনী পুষত এবং প্রতিকারের জন্য জনগণের সামনে কোনো রাস্তা ছিল না। আদালত বস্তুত ছিল তাদের নাগালের বাইরে। উৎপীড়ক জমিদার ও নীলকরদের থাবা থেকে কৃষক-জনতাকে রক্ষার লড়াই করে ফরায়েজী আন্দোলন। এসব অত্যাচারকে চ্যালেঞ্জ করে এবং কৃষক ও মজলুম প্রজার অধিকারের পক্ষে দাঁড়ায় শক্তভাবে। বাড়তি ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করে কৃষককে রুখে দাঁড়ানোর পটভূমি ও শক্তি জোগান দেয়, ঐতিহ্য তৈরি করে। ব্রিটিশ শাসক ও জমিদার শ্রেণীর সর্বময় ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকে সংগঠিত এ আন্দোলন। গণজীবনে এর প্রভাব ও আবেদন তৈরি হয়। পূর্ব বাংলা-আসামের গ্রামেগঞ্জে, লোকজীবনে সে একাত্ম হয়, নিপীড়িতের কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়, তাদের সরবরাহ করে জীবনীশক্তি।
দেশের ভেতরে সামাজিক শাসনের বিকল্প শৃঙ্খলা তৈরি করে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আপন কর্তৃত্বে নিয়ে নেন ফরায়েজীরা। গড়ে তোলেন বিচার, নিরাপত্তা ও সমাজনৈতিক নিজস্ব পরিকাঠামো। জেমস ওয়াইজের মতে, পূর্ব বাংলার পঞ্চায়েতগুলো জনগণের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ফরায়েজী গ্রামগুলোতে সংঘটিত হিংসাত্মক বা মারামারির কোনো ঘটনা কদাচিৎ নিয়মিত আদালত পর্যন্ত গড়াত। ফরায়েজীপ্রধান ঝগড়া-বিবাদ নিষ্পত্তি করতেন, তাৎক্ষণিকভাবে বিচারকাজ সম্পন্ন করতেন এবং যেকোনো হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিষ্টান তার পাওনা আদায়ের জন্য ফরায়েজী নেতার কাছে অভিযোগ পেশ করতেন। জমিদারদের বিরুদ্ধে ফরায়েজীদের সহায়তা লাভের জন্য এ আন্দোলনে যোগ দেন বিপুলসংখ্যক হিন্দু ও দেশীয় খ্রিষ্টান।
ফরায়েজী এ সাংগঠনিকতাকে বিকল্প রাষ্ট্রের আয়োজন হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে জমিদার শ্রেণী। ১৮৩৭ সালে তারা শরীয়তউল্লাহকে তিতুমীরের মতো স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের উদ্যোগের জন্য অভিযুক্ত করে। ফরায়েজীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় অসংখ্য মামলা। ইউরোপীয় নীলকররা তাদের সহায়তা করে। কিন্তু ফরায়েজী প্রচেষ্টাগুলো ছিল সুচিন্তিত। রাষ্ট্র ও প্রচলিত আইনকে সরাসরি লঙ্ঘন করছিল না তাদের প্রয়াস। দিন শেষে অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। আদালত তা খারিজ করে দেন। হান্টার উল্লিখিত গ্রাম পোড়ানো, প্রজা হত্যা ইত্যাদির অভিযোগও হাজী শরীয়তুল্লাহর বিরুদ্ধে ছিল না। যদিও উত্তেজনা বিস্তারের দায়ে কিছুদিন তাকে পুলিশি হেফাজতে রাখা হয় অন্য এক মামলায়। শরীয়তুল্লাহ পরবর্তী ফরায়েজী নেতা মুহসেন উদ্দীন দুদু মিয়ার নেতৃত্বে জমিদারবিরোধী প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের ওপর মূলত হান্টারের এ আরোপ।
দুদু মিয়া অত্যাচার থামাতে কানাইপুরের কুখ্যাত শিকদার পরিবার ও ফরিদপুরের ঘোষদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। জমিদার মদন ঘোষ নিহত হন এক লড়াইয়ে। ১১৭ জন ফরায়েজী আন্দোলনকারী গ্রেফতার হন এবং তাদের মধ্যে ২২ জন দায়রা জজ কর্তৃক সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।
জমিদার-নীলকররা তার বাড়িতে হামলা করে। তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। প্রতাপশালী নীলকর এন্ড্রু ডানলপ ছিলেন এর নেতৃত্বে। তার গোমস্তা ছিলেন কালীপ্রসাদ কাঞ্জিলাল। ১৮৪৬ সালের অক্টোবর মাসে পাঁচ্চরের হিন্দু বাবুদের সাথে মিলে আনুমানিক সাত-আট শ’ লোক নিয়ে কাঞ্জিলাল বাহাদুরপুরে দুদু মিয়ার বাড়ি আক্রমণ করেন। তারা তার ঘরের সামনের দরজা ভেঙে ফেলেন, চারজন পাহারাদারকে হত্যা করেন এবং অন্যদের মারাত্মকভাবে জখম করে নগদ অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী মিলিয়ে প্রায় দেড় লাখ টাকা মূল্যের সম্পদ কেড়ে নেন। হান্টারের বিবরণে এ হত্যা ও আক্রমণ হত্যা হয় না, এ অন্যায় জায়গা পায় না তার বিচারে। হান্টার কি একে ন্যায্য মনে করতেন, যেমনটি করেছিল তখনকার স্থানীয় প্রশাসন। তারা কাঞ্জিলালের সাথে সংঘর্ষের জন্য গ্রেফতার করেছিল দুদু মিয়া ও তার সাথীদের। যদিও পরবর্তী বিচারে তিনি ও তার সাথীরা বেকসুর খালাস পান।
আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গণমানুষের লড়াই-সংগ্রামে ইসলামের অবশ্যম্ভাবী ভূমিকাকে প্রতিফলিত করতে সক্রিয় থাকে ফরায়েজী আন্দোলন। সেই কৃষকদের ঘুরে দাঁড়ানোর পথ দেখায়, যাদের মানবসত্তাকে পদাঘাত করছিল ঔপনিবেশিক শক্তি ও তাদের দেশীয় অনুচর জমিদার গোষ্ঠী। তারা কৃষিজ উৎপাদন করবে। কিন্তু লাভবান হবে শুধু শোষক শ্রেণী। এমনকি ধান-পাট ইত্যাদির বদলে কৃষককে বাধ্য করবে নীল চাষে। যার সাথে কৃষকের বিন্দুমাত্র স্বার্থ জড়িত নেই, আছে কেবল নীলকর ও কলোনি শাসকদের স্বার্থ। কৃষক শ্রম, অর্থ ও জীবন বিনিয়োগ করবে, পাবে না কিছুই। সবকিছুর রক্ত-মাংস শুষে নেবে কোম্পানি ও জমিদারি। আবাদ করবে যে কৃষক, তার স্থান হালের বলদের অধিক নয়। আপন স্বার্থ ও প্রয়োজনকে উপেক্ষা করতে সে রাজি না হলে সব ধরনের অত্যাচার তার জন্য অপেক্ষা করবে, এমনকি মৃত্যু!
সেই কৃষকদের নিয়ে জমিদারদের কালচারকে, আচারকে, প্রত্যাখ্যান করে স্বকীয় আচার ও সংস্কৃতির পুনরোজ্জীবন আদতেই ছিল প্রবল এক বিদ্রোহ। হান্টার এর মূল্য ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব জানবেন না, তা তো নয়। অতএব ঔপনিবেশিক কেরানি হিসেবে ঠিকই তিনি একে বিপজ্জনক আখ্যা দেন। কারণ জানা যায় স্বয়ং হান্টারের ভাষ্যে। লড়াকুদের সাংগঠনিক দক্ষতা ও সক্ষমতার প্রসঙ্গ হাজির করেন তিনি। জানান, ‘দক্ষ সংগঠনের মাধ্যমে তারা মুরিদদের তাকিদে যেখানে প্রয়োজন, সেখানেই আস্তানা স্থাপন করতে পারত। প্রত্যেক জেলাতেই একজন করে প্রচারক নিযুক্ত হয়। ভ্রাম্যমাণ মিশনারিরা মাঝে মধ্যে এসব জেলা সফরকালে সেখানকার স্থায়ী প্রচারকদের উদ্যম জাগ্রত রাখতে থাকে।’
‘অর্থ সংগ্রহ ব্যবস্থাটা সহজ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। গ্রামগুলোকে বিভিন্ন আর্থিক এলাকায় বিভক্ত করে প্রত্যেক এলাকার জন্য একজন করে প্রধান ট্যাক্স আদায়কারী নিয়োগ করা হয়। যে গ্রামের জনসংখ্যা খুব বেশি, সেখানে একাধিক আদায়কারী নিয়োগ করা হয় এবং তার মধ্যে একজন মৌলবি থাকতেন যিনি সমাজে ইমামতি করতেন। একজন জেনারেল ম্যানেজার রাখা হয়, যিনি মুসলমানদের দুনিয়াবি কাজের তদারক করতেন। এ ছাড়া একজন অফিসার থাকতেন, তার কাজ ছিল বিপজ্জনক চিঠিপত্র বিলিবণ্টন ও রাজদ্রোহমূলক খবরাখবর আদান-প্রদান করা।...’
ব্রিটিশ কলোনির স্থানীয় লাঠিয়াল ছিল জমিদার শ্রেণী। তাদেরকে, তাদের শোষণ ও স্বেচ্ছাচারকে সবলে ‘না’ বলার মানে ছিল গোটা ব্রিটিশ কলোনিকে না বলা। অতএব হাজী শরীয়তুল্লাহ এ দেশকে দারুল হারব তথা শত্রুকবলিত দেশ বা যুদ্ধভূমি হিসেবে আবদুল আজিজ দেহলবীর ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করলেন। এর স্পষ্ট দাবি ছিল শত্রু তাড়ানো। মানে স্বাধীনতা।
কলোনি শাসক ও তার শিখণ্ডিদের চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আত্মপরিচয়ভিত্তিক নিজস্বতার সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূগোল নির্মাণ করে ফরায়েজী আন্দোলন এদেশে গণজীবনে সত্যিকার ইসলামের প্রতি অভিমুখের নবযুগ ও নবসক্রিয়তা কেবল আনেনি, বরং বৃহত্তর আত্মসত্তা ও স্বাধীনতার পথে জাতিগত প্রস্তুতির নতুন যুগের উদয় ঘটিয়েছে। ১৮৪০ সালে হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর তার ছেলে মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়ার হাত ধরে ফরায়েজী আন্দোলন আমাদের আত্মপরিচয়, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা এবং সত্যিকার ধর্মজীবনের উত্থানের প্রয়াসের পাশাপাশি স্বাধীকারচেতনার নতুন জমি তৈরি করে দেয়, যার ওপর পা রেখেছে কৃষিপ্রধান বাঙালি মুসলমানের পরবর্তী অগ্রগতি!
-এটি