

|
ভূমিকম্পের ছায়া, বাংলাদেশ হোক সচেতন ও প্রস্তুত
প্রকাশ:
২১ নভেম্বর, ২০২৫, ০৫:১৫ বিকাল
নিউজ ডেস্ক |
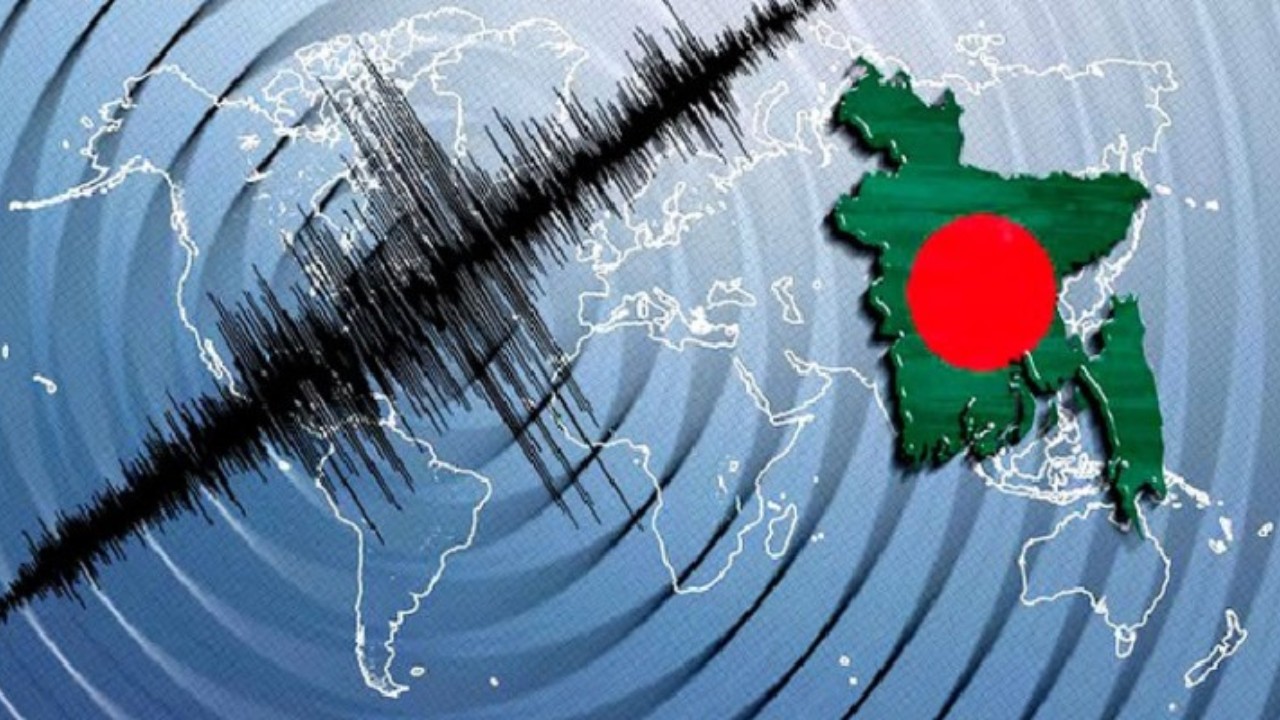
||ডা.মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ||
বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রকৃতির কারণে দীর্ঘদিন ধরেই ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সক্রিয় ভূতাত্ত্বিক ফল্ট লাইন বা ভাঙা ভূপৃষ্ঠের চাপে সৃষ্ট ভূমিকম্পীয় কার্যকলাপ বাংলাদেশের জন্য এক অনিবার্য বাস্তবতা। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান দেখায়, গত ২৩ মাসে দেশের ভেতরেই ১৯টি ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। এই সংখ্যা যেমন উদ্বেগ বাড়ায়, তেমনি বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা আরও গভীর করে তোলে যে, বড় ধরনের ভূমিকম্পের ঝুঁকি প্রতিনিয়ত বাড়ছে।
২৩ মাসে দেশে ১৯ ভূমিকম্প:
শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ৫ দশমিক ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।শক্তিশালী এই ভূমিকম্পে ২১ নভেম্বর দুপুর ২ টা পযন্ত ৩ জন নিহত ও ৮৫ জন আহত হওয়ার প্রাথমিক ও অনানুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া গেছে।এটাকে দেশের ইতিহাসে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প। এর আগে সর্বশেষ চলতি বছরের ২১ সেপ্টেম্বর দেশের অভ্যন্তরে ভূমিকম্প হয়। সেদিন দুপুর ১২টা ১৯ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এটির উৎপত্তিস্থল ছিল সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলা। ঢাকা থেকে উৎপত্তিস্থলের দূরত্ব ছিল ১৮৫ কিলোমিটার।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের আজ ২১ তারিখ পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে ১৯টি ভূমিকম্প হয়।
এর মধ্যে শুধু গত ১৪ মাসে (২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের ২১ তারিখ পর্যন্ত হয়েছে ১১টি ভূমিকম্প। এছাড়া ২০২৪ সালে ১২টি ভূমিকম্প হয়। আর চলতি ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের ২১ তারিখ পর্যন্ত দেশে ৭টি ভূমিকম্প হয়েছে।
তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পগুলোর মধ্যে সিলেটেই ঘটেছে সর্বাধিক ৮টি। এছাড়া দিনাজপুরে ২টি, রংপুরে ২টি, পাবনায় ১টি, কুমিল্লায় ১টি, শরীয়তপুরে ১টি এবং টাঙ্গাইলে ১টি, রাঙ্গামাটিতে ১টি, চুয়াডাঙ্গায় ১টি ভূমিকম্প হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প ছিল শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলায়, ২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর ঢাকা থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৪.১।
তবে ২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর এরপর আজ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।আর বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রথম বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানে ১৫৪৮ সালে। এর ফলে বর্তমানে চট্টগ্রাম ও সিলেটের অবস্থান যেখানে, এই অঞ্চলে নানা জায়গায় মাটি ফেটে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। সেখান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত কাদা-পানি বেরোনোর তথ্যও পাওয়া যায়। তবে এই ভূমিকম্পে বর্ণনায় হতাহতের কোনো তথ্য লিপিবদ্ধ হয়নি।
পরবর্তী শতকে ১৬৪২ সালে এক শক্তিশালী ভূমিকম্পে সিলেট জেলার অনেক দালান-কোঠা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সেবারও মানুষের প্রাণহানীর খবর পাওয়া যায়নি।
বাংলাদেশের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হওয়া অন্যতম বড় ভূমিকম্পটি ঘটে ১৭৬২ সালের এপ্রিল মাসে। ১৯০৮ সালের 'ইস্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার চিটাগাং'-এর তথ্য অনুযায়ী, ১৭৬২ সালের ভূমিকম্পে চট্টগ্রাম জেলার অনেক জায়গায় মাটি ফেটে প্রচুর পরিমাণে কাদা-পানি ছিটকে বেরোয়। 'পর্দাবন' নামক জায়গায় একটি বড় নদী শুকিয়ে পড়ার বর্ণনাও পাওয়া যায় তখন। 'বাকর চনক' নামের এক অঞ্চলের প্রায় ২০০ মানুষ তাদের গৃহপালিত প্রাণীসহ পুরোপুরি নিমজ্জিত হয় সমুদ্রগর্ভে। ভূমিকম্পের পরবর্তী সময়ে ভূখণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় সৃষ্টি হয় অতল গহ্বরের। মাটির নিচে কয়েক হাত গভীরতায় দেবে গিয়ে কিছু কিছু গ্রাম ভেসে যায় পানিতে।
কথিত আছে সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে দুটি আগ্নেয়গিরি উৎপন্ন হয়েছিল সেই ভূমিকম্পের প্রভাবে। যদিও পরবর্তীতে আর চিহ্নিত করা যায়নি নির্দিষ্ট নামে বর্ণিত সেই স্থানগুলোকে। চট্টগ্রামের বর্তমান বাহারছড়া নামক জায়গাটিকে আঠারো শতকের সেই সময়ে 'বাকর চনক' নামে অভিহিত করা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।
১৭৬২ সালের এই ভূমিকম্পে চট্টগ্রামের পাশাপাশি ঢাকাতেও ভয়াবহ ভূকম্পনের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে ১৯১২ সালের 'ইস্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার ঢাকা'তে। জেমস টেইলরের 'আ স্কেচ অব দ্য টপোগ্রাফি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস অব ঢাকা'র বর্ণনা অনুযায়ী, ঢাকার বিভিন্ন নদী আর ঝিলের পানিতে প্রবল আলোড়ন দেখা গেছে সেই ভূমিকম্পের সময়ে। পানির স্তরও সাধারণ সময়ের চেয়ে বেশি উঁচু হয়ে গিয়েছিল। ভূকম্পন শান্ত হলে পানি নিচে নেমে যাওয়ার পর অসংখ্য মরা মাছ ছড়িয়ে ছিল জলাশয়ের পাড়ে।
ভূপৃষ্ঠের প্রবল আলোড়নের পাশাপাশি এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল ভূগর্ভস্থ শব্দ। অসংখ্য বাড়িঘর ভেঙে পড়েছিল ভূমিকম্পের ফলে। প্রাণ হারিয়েছিল প্রায় ৫০০ মানুষ।
ইস্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার ঢাকা'র একই সংখ্যায় পাওয়া যায় ১৭৭৫ ও ১৮১২ সালের শক্তিশালী ভূমিকম্পের বর্ণনা। ১৮১২ সালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বেশ কিছু ঘরবাড়ি আর দালান-কোঠা। বাংলাপিডিয়া-র তথ্য অনুযায়ী, ১৭৭৫ সালের ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়েছে ঢাকার আশেপাশের অঞ্চলে আর ১৮১২ সালের ভূমিকম্পটি হয়েছিল সিলেটে। তবে উভয় ভূমিকম্পেই হতাহতের কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি।
১৮৬৫ সালের শীতকালে আরেকটি শক্তিশালী ভূমিকম্পের বর্ণনা পাওয়া যায় ১৯১২ সালের 'ইস্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার চিটাগাং'এ। সীতাকুণ্ডের এক পাহাড় ফেটে বালি আর কাদা বেরোয় সেই সময়। তবে আর কোনো গুরুতর ক্ষতির তথ্য মেলেনি এই ভূমিকম্পে।
১৮৮৫ সালে মানিকগঞ্জে আঘাত হানা প্রায় ৭ মাত্রার ভূমিকম্পটি পরিচিত 'বেঙ্গল আর্থকোয়েক' নামে। এর সম্ভাব্য উপকেন্দ্র ছিল ঢাকার ১৭০ কিলোমিটার দূরবর্তী সাটুরিয়ার কোদালিয়ায়। এই ভূমিকম্পের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে ভারতের বিহার, সিকিম, মণিপুর ও মিয়ানমারেও অনুভূত হয়েছিল কম্পন। ঢাকা, ময়নমনসিংহ, শেরপুর, পাবনা, সিরাজগঞ্জের অনেক দালানকোঠা, স্থাপত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেবার। তবে এতে প্রাণহানীর কোনো সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি।
১৮৯৭ সালের ১২ জুন সংঘটিত বিধ্বংসী ভূমিকম্পটি পরিচিত 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থকোয়েক' নামে। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ধারণা করা হয় প্রায় ৮। ১৯২৩ সালের 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার পাবনা'য় বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পে সিরাজগঞ্জে উপবিভাগীয় অফিসের উপরের তলা, কারাগার, ডাকঘরসহ নানা স্থাপনা ধ্বংস হয়। প্রায় সকল দালান স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভীষণভাবে। অ্যান্ড্রু ইউল অ্যান্ড কোং এর পাটের ব্যাগের ফ্যাক্টরি ধূলিসাৎ হয়ে যায় এই ধাক্কায়। কোম্পানিটি তাদের ব্যবসাই গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয় এরপর। পাবনার কোর্ট হাউজসহ অন্যান্য ইটের স্থাপনাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভূপৃষ্ঠের নানা স্থানে চির ধরে, অনেক কূয়া পরিপূর্ণ হয় ভূ-তল থেকে উঠে আসা পলিমাটি আর বালিতে।
'ইস্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার চিটাগাং' থেকে জানা যায়, ১৮৯৭ সালের এই ভূমিকম্পটি পূর্বে দক্ষিণ লুসাই পর্বতমালা থেকে শুরু করে পশ্চিমে শাহাবাদ পর্যন্ত সমগ্র বাংলা জুড়ে অনুভূত হয়েছিল। যার সম্ভাব্য মূলকেন্দ্র ছিল আসামের চেরাপুঞ্জির কাছাকাছি। ভূমিকম্পের স্থায়ীত্বকাল ছিল জায়গাভেদে ছয় সেকেন্ড থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত। চট্টগ্রামে স্থায়ী ছিল সবচেয়ে বেশি সময় ধরে।
'ইস্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার ঢাকা'র তথ্য মতে, উক্ত ভূমিকম্প ঢাকা শহরের অনেক উল্লেখযোগ্য স্থাপনার ক্ষতিসাধন করেছিল। সে তুলনায় প্রাণহানীর সংখ্যা ছিল বেশ কম। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি স্থাপনাগুলোর মেরামত বাবদ সেসময় খরচ হিসাব করা হয়েছিল প্রায় দেড় লাখ রূপি।
বাংলাপিডিয়া-র তথ্য অনুযায়ী, ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে শুধু সিলেট জেলাতেই মৃতের সংখ্যা ছিল ৫৪৫। ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিঘ্নিত হয় এর কারণে। রাজশাহীসহ পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য জেলাও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখনকার হিসাবে শুধু অর্থ-সম্পত্তির ক্ষতিই হয়েছিল প্রায় ৫০ লাখ টাকা।
১৯১৮ সালে প্রায় ৭.৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয় শ্রীমঙ্গলে। যা শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প নামেই পরিচিত। মিয়ানমার ও ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলেও অনুভূত হয়েছিল এই ভূমিকম্প। শ্রীমঙ্গলের অনেক দালান-কোঠা ধ্বংস হয়েছিল এই ভূকম্পনে।
১৯৫০ সালের ১৫ আগস্ট আঘাত হানে আসাম ভূমিকম্প। বিংশ শতকের অন্যতম ভয়ানক এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৮.৭। বাংলাদেশের নানান অঞ্চলে এটি অনুভূত হলেও তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি দেশে।
১৯৯৭ সালের ২২ নভেম্বর চট্টগ্রামে ৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্প ঘটে। এতে শহরের নানান স্থাপনায় ফাটল ধরে।
বিংশ শতকে বাংলাদেশের শেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্পটি হয় মহেশখালী দ্বীপে। ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসের সেই ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল এই দ্বীপেই। ৫.২ মাত্রার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দ্বীপের অনেক বাড়িঘর।
কেন বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ
বাংলাদেশ মূলত তিনটি প্রধান সক্রিয় ফল্ট লাইনের চাপে রয়েছে:
১. বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় মেগা থ্রাস্ট ফল্ট – এটি মিয়ানমার থেকে শুরু হয়ে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল ও বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।
২. হিমালয়ান ফ্রন্টাল ফল্ট – উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই ফল্ট লাইন নেপাল, ভুটান ও উত্তর ভারতের ভূমিকম্পীয় কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে।
৩. দাউকি ফল্ট ও সিলেট অঞ্চল – উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে অবস্থিত এই ফল্ট লাইন বিশেষভাবে সক্রিয় এবং ঘনঘন ভূমিকম্পের উৎস।
এই ভূতাত্ত্বিক অবস্থান বাংলাদেশের জন্য দ্বিগুণ ঝুঁকি তৈরি করে। একদিকে বাইরের ভূমিকম্প আমাদের প্রভাবিত করে, অন্যদিকে দেশের ভেতরে নিজস্ব ফল্ট লাইনও নড়াচড়া করছে। ফলে বাংলাদেশের শহরাঞ্চল, বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং উত্তরাঞ্চলীয় কিছু জেলা সরাসরি ঝুঁকির মুখে।
নগরায়ণ ও দুর্বল অবকাঠামো: ঝুঁকির মূল কারণ
শুধু ভূতাত্ত্বিক কারণ নয়, বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হলো অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও দুর্বল অবকাঠামো। ঢাকা শহর পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ শহর। আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকায় যদি ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হয়, তাহলে কয়েক লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হতে পারে এবং লাখ লাখ মানুষ আহত বা গৃহহীন হয়ে পড়তে পারে।
কারণগুলো হলো— * ভবন নির্মাণে সঠিক কোড না মানা। * পুরোনো ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের আধিক্য। * সরু রাস্তা ও অপর্যাপ্ত উন্মুক্ত স্থান, যেখানে মানুষ আশ্রয় নিতে পারবে না। * জরুরি উদ্ধার ও চিকিৎসা সেবার সীমিত সক্ষমতা।
গ্রামীণ এলাকায় কাঠামো তুলনামূলকভাবে সহজ হলেও, শহরে বহুতল ভবন ও অনিয়ন্ত্রিত স্থাপনা ভূমিকম্পের সময় মৃত্যুফাঁদে পরিণত হতে পারে।
ভূমিকম্প ও মানুষের প্রস্তুতির অভাব
বাংলাদেশে ভূমিকম্প সচেতনতা তুলনামূলকভাবে কম। ভূমিকম্পের সময় কী করতে হবে—এই মৌলিক ধারণাও অধিকাংশ মানুষের নেই। স্কুল, কলেজ বা অফিস পর্যায়ে ভূমিকম্প মহড়া সচরাচর হয় না। গণপরিবহন, হাসপাতাল বা বাজারের মতো জনবহুল স্থানে কোনো জরুরি পরিকল্পনা নেই। ফলে একটি বড় ভূমিকম্প ঘটলে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ করে তুলতে পারে।
অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা
একটি বড় ভূমিকম্প শুধু প্রাণহানি নয়, দেশের অর্থনীতিতেও গভীর ক্ষত তৈরি করবে। গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকায় যদি ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হয়, তবে শুধু ভবন ধসেই প্রায় অর্ধেক আর্থিক কার্যক্রম ভেঙে পড়তে পারে। ব্যাংক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, পোশাকশিল্প, এমনকি তথ্যপ্রযুক্তি খাতও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
এছাড়াও, সড়ক ও সেতুর মতো অবকাঠামো ধসে গেলে দেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ ব্যাহত হলে শিল্প উৎপাদন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এক কথায়, একটি বড় ভূমিকম্প বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে কয়েক দশক পিছিয়ে দিতে পারে।
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব
ভূমিকম্প কেবল প্রাণহানি ও অর্থনীতির ক্ষতি করে না, সামাজিক কাঠামোকেও দুর্বল করে দেয়। বাস্তুচ্যুত মানুষরা গ্রামীণ বা শহুরে আশ্রয়কেন্দ্রে ভিড় করলে নতুন করে স্বাস্থ্যঝুঁকি, খাদ্য সংকট ও শিক্ষার বিঘ্ন দেখা দেবে। শিশুরা পড়াশোনার বাইরে চলে যাবে, নারীরা নিরাপত্তাহীনতার শিকার হবে এবং বেকারত্ব বাড়বে। একটি বড় ভূমিকম্প তাই সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণও হতে পারে।
আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা
২০০৫ সালের পাকিস্তানের কাশ্মীর ভূমিকম্প কিংবা ২০১৫ সালের নেপালের ভূমিকম্প থেকে স্পষ্ট হয়েছে, অপ্রস্তুত অবস্থায় মধ্যম মাত্রার ভূমিকম্পও ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। নেপালে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় ৯ হাজার মানুষ মারা যায়, লক্ষাধিক মানুষ আহত হয় এবং কয়েক কোটি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। পাকিস্তানেও প্রাণহানির সংখ্যা কয়েক দশক পেরিয়ে আজও জাতীয় স্মৃতিতে গভীর ক্ষত তৈরি করে রেখেছে।
বাংলাদেশের অবস্থা এই দেশগুলোর চেয়েও ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ আমাদের জনঘনত্ব বেশি, রাজধানী অতি জনবহুল, এবং ভবন নির্মাণে নিরাপত্তা মানদণ্ড প্রায়ই উপেক্ষিত হয়।
সরকারের ভূমিকা ও নীতি বিশ্লেষণ
সরকার ইতিমধ্যে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, যেমন: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ভূমিকম্প মহড়া, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বাড়ানো এবং কিছু গবেষণা প্রকল্প। তবে এগুলো এখনও অপর্যাপ্ত।
সমস্যাগুলো হলো— * নীতিমালা থাকলেও প্রয়োগ দুর্বল। * স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর সীমিত সরঞ্জাম।
* ভবন নির্মাণে দুর্নীতি ও অবহেলা। * গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে বাজেট সীমাবদ্ধতা।
করণীয়
বাংলাদেশকে সম্ভাব্য ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবিলায় জরুরি ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে:
১. ভবন নির্মাণে ভূমিকম্প সহনশীল কোড প্রয়োগ – নতুন সব স্থাপনা নির্মাণে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। পুরোনো ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোর জরুরি সংস্কার বা ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নিতে হবে।
২. নগর পরিকল্পনা ও খোলা জায়গা সংরক্ষণ – প্রতিটি বড় শহরে পর্যাপ্ত খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান ও আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে হবে, যেখানে ভূমিকম্পের সময় মানুষ নিরাপদে জড়ো হতে পারে।
৩. সচেতনতা বৃদ্ধি ও মহড়া – স্কুল, কলেজ, অফিস ও গণপরিবহন পর্যায়ে নিয়মিত ভূমিকম্প মহড়া চালু করা জরুরি। গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে প্রশিক্ষিত করতে হবে।
৪. জরুরি সেবা ও উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধি – দমকল, সিভিল ডিফেন্স, হাসপাতাল এবং সেনাবাহিনীকে ভূমিকম্প পরিস্থিতির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে প্রস্তুত রাখতে হবে।
৫. ভূমিকম্প গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়ন – দেশে ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। ভূমিকম্প পূর্বাভাস প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে অন্তত কয়েক সেকেন্ডের আগাম সতর্কবার্তা দেওয়া সম্ভব হলে তা অনেক জীবন বাঁচাতে পারে।
৬. আঞ্চলিক সহযোগিতা – ভারত, নেপাল, ভুটান ও মিয়ানমারের সঙ্গে ভূমিকম্প তথ্য বিনিময় ও সমন্বিত প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরি। কারণ ভূমিকম্পের প্রভাব জাতীয় সীমানা মানে না।
পরিশেষে বলতে চাই, বাংলাদেশে ঘনঘন ভূমিকম্প হওয়া কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গত ২৩ মাসে দেশের ভেতরে অন্তত ১৯টি ভূমিকম্প ঘটেছে, যা প্রমাণ করে যে ভূতাত্ত্বিক সক্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রাকৃতিক ঝুঁকির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, দুর্বল অবকাঠামো এবং জনগণের প্রস্তুতির অভাব। শহরগুলোতে সঠিক মানদণ্ড মেনে নির্মাণ না হওয়া, জনবসতি এলাকা ক্রমশ ঘন হওয়া এবং জরুরি ব্যবস্থা নাও থাকা বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।
যদি এই সমস্যাগুলো সমাধান না করা যায়, তবে একটি বড় ভূমিকম্প শুধু লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটাবে না, দেশের অর্থনীতিকেও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ক্ষয়ক্ষতির পরিধি শুধু নগর এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং দেশের বিভিন্ন অংশে প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সড়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ভেঙে পড়লে পুনর্গঠন প্রচেষ্টা অনেক দেরিতে এবং ব্যয়সাপেক্ষ হবে।
অতএব এখনই প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ। সরকারের পাশাপাশি নগর পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী, গণমাধ্যম এবং সাধারণ মানুষ—সবাইকে এই প্রস্তুতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। ভূমিকম্প কখন ঘটবে তা কেউ নির্দিষ্টভাবে বলতে পারবে না, তবে সচেতনতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলার পরিকল্পনা, জরুরি সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষণ থাকলে ক্ষয়ক্ষতি অনেক কমানো সম্ভব।
বাংলাদেশের জন্য ভূমিকম্প এখন আর শুধু বৈজ্ঞানিক বা তাত্ত্বিক আলোচনা নয়। এটি জাতীয় নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। আমাদের সময়মত প্রস্তুতি, সচেতনতা এবং দায়িত্বশীল পদক্ষেপই দেশের মানুষ এবং অর্থনীতিকে বড় বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।
লেখক: কলাম লেখক ও গবেষক
প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান: জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি
ইমেইল: drmazed96@gmail.com
এলএইস/
|